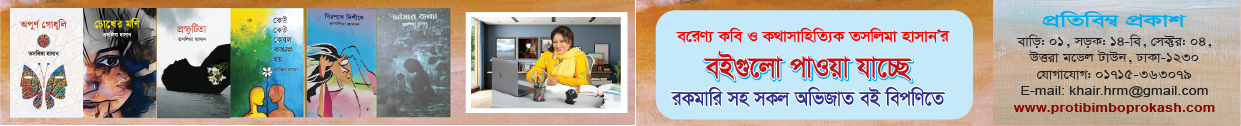এক কাল বৈশাখীর ঝড়ে
যুথিকা বড়ুয়া
প্রবাসী জীবনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রত্যেক বছর পূজা-পার্বন কিংবা কোনো আনন্দ উৎসবের দিন ঘনিয়ে এলেই দেশের টানে মনটা কেমন আনচান করে ওঠে। বিশেষ করে বাংলা নববর্ষ। তখন মুহূর্তে ছুটে চলে যায়, কৈশোরের আনন্দ-কোলাহল মুখরিত হাজার মায়া ঘেরা সবুজ শ্যামল বাংলার মুখ আমাদের সেই নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। চকিতে প্রতিবিম্বের মতো মনের আয়নায় ভেসে ওঠে, উষার প্রথম প্রহরের তরুণ সূর্যের কাঁচাসোনা রোদমাখা দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল গাঢ় সবুজ মাঠ। কোথাও কচুরীপানাভরা পুকুর, খাল-বিল, নালা-নর্দমা আর ছোট্ট ছোট্ট জলাশয়। যেখানে বর্ষার জল জমে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙাচি আর শোলমাছের পোনারা কিলবিল করতো। আমরা সঙ্গী-সাথিরা সবাই দলবেঁধে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে নেমে পড়তাম মাছ ধরতে। কখনো বা প্রবল ঝড়ের মুখে ছুটে যেতাম, পাড়ার ঝন্টুদের বিশাল আমগাছতলায় কাদায় লেপটে পড়ে থাকা কাঁচা-পাকা আম আর জামরুলের সন্ধানে। কোনো কোনো সময় আমাদের মাথার উপরেই টপাটপ ঝড়ে পড়তো। আমরা তখন মনের আনন্দে দিশা হারিয়ে দুই হাতে বুকভরে কুড়োতাম। ততক্ষণে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন ঝন্টুর মা, প্রভারানী দেবী। তিনি ছিলেন সাংঘাতিক কৃপণ এবং হিংসুটে গোছের মন-মানসিকতা। ওনার গাছের আম কাউকে স্পর্শ করতে দিতেন না। নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পাড়ার কিশোর কিশোরীরা কেউ তা গ্রাহ্য করতো না! ওনার অলক্ষ্যে আমরাও চুপিচুপি আমবাগানে ঢুকে পড়তাম। কিন্তু উনি টের পেলে আর রক্ষে রাখতেন না। গরুতাড়া করতেন, গালি-গালাজ করতেন। মুখে একগাল পান নিয়ে উত্তপ্ত মেজাজে বলতেন,-‘তগোর এত্তবড় সাহস, নিষেধ সত্বেও তরা ঢুকছস! তগোর শরীলে ডর-ভয়ও কী নাই! গাছেরডাল একখান্ ভাইঙ্গা পড়লে ফাইট্যা যাইব গিয়া তগোর মাথা। কই গেল ঝন্টু, হেইডাই হইল গিয়া যত্ত নষ্টের গোড়া। ছ্যামড়া দলবল আইন্যা উৎপাত করস। চিল্লাচিল্লি করস। আমার কত্ত সাধের আমগুলারে ধংস করস। আয় ঘরে, আজ দিমু তর ঠ্যাং ভাইঙ্গা!’
ঝন্টুই ছিল নাটের গুরু। বদের হাড্ডি। নিজেই ওর সঙ্গী-সাথিদের ডেকে নিয়ে গিয়ে উৎপাত করতো। হৈ চৈ করতো। মায়ের সাড়া-শব্দ পেলেই সবাইকে ভাগিয়ে দিতো। আজ যেখানে বসত বাড়ি, হাই-রাইজ্ বিল্ডিং তৈরী হয়ে কী নিদারুণ ঝক্ঝক্ েতকতকে একটি সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়েছে। অতীতের সেই গ্রাম্য পরিবেশের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু কৈশোরে গ্র্রামীণ বাংলার মাটিতে ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনের অমলিন স্মৃতিগুলি কখনো কী ভোলা যায়! কখনো কী ভোলা যায়, প্রবল বর্ষণের ছটায় পদ্মদীঘির শাফলা ফুলের পাঁপড়ি মেলে মনমাতানো নাচনের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য!
না, কখনো ভোলা যায় না। তেমনি কখনোই ভোলা যায় না, বিশাল সবুজ বিলের মাঝে কচুবনের গা-ঘেষে কয়লার ইঞ্জিনে চলন্ত রেলগাড়ির হৃদয় কাঁপানো জোরালো বাঁশি আর ঝিকঝিক্ শব্দের এক অদ্ভুত আকর্ষণে ছুটে গিয়ে যেদিন চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল আমাদের ছেলেবেলার সাথী ঝন্টুর দৃষ্টিশক্তি।
অনেক বছর আগের কথা। তখন কত আর বয়স আমাদের। সাত আট হবে। বিবেক-বুদ্ধির বিকাশই ঘটেনি। মুক্ত-বিহঙ্গের মতো বন্ধনহীন, চিন্তাহীন মুক্ত জীবন। কোনো পিছু টান নেই। কত আনন্দের। তখন আমাদের ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বোধ-জ্ঞান কিছু ছিল না। ঝন্টুই আমাদের ইন্ধন জোগাতো, আমাদের গাইড করতো। উৎসাহ দিতো। রাত পোহালেই শুরু হয়ে যেতো ওর পাঁচালী। আমরাও নির্বোধের দল ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ণোদ্যমে মেতে উঠতাম আনন্দ-কোলাহলে। দিগন্তের পশ্চিমপ্রান্তে ক্লান্ত সূর্য্য কখন যে অস্তাচলে ঢলে পড়তো আমাদের হুঁশ-জ্ঞানই থাকতো না। আমরা মনের আনন্দে খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে ভেসে বেড়াতাম।
ঝন্টু প্রতিদিনই অবাধ্যতা এবং বেপরোয়ার কারণে মায়ের বকুনি খেতো। কোনো কোনো দিন কাঁচা বাঁশের সরু কঞ্চি দিয়ে মায়ের পিটুনি খেতো। যেমন ছিল অতিরিক্ত চঞ্চল, দুরন্ত তেমনি দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা। লেখাপড়াতেও একেবারে অষ্টরম্ভ। কোনরকমে ভাতদু’টো গোগ্রাসে মুখে দিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামমাত্র স্কুলে ছোটা, ক্লাস করা। তারপর ওর নাগাল পায় কে! কাঁধের ব্যাগটা আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে পাড়ায় পাড়ায় টো টো কোম্পানী করে ঘুরে বেড়ানোই ছিল ঝন্টুর ডেলি রুটিন। আর ছুটিরদিনে সারা পাড়া মাথায় নিয়ে উদয়াস্থ চলতো ওর রাজত্ব। হনুমানের মতো তর তর করে আমগাছের আগায় উঠে শীশ্ দিয়ে আমাদের সকলকে একটা জায়গায় একত্রিত করতো। আমরা লুকোচুরি খেলতাম। ডাঙ্গুলি খেলতাম। আরো কত কি! কিন্তু রেলগাড়ির ঝিক ্ঝিক্ শব্দ আর বাঁশি শুনলে ঝন্টুকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। সবার অলক্ষ্যে একাই ছুটে চলে যেতো কচুবনের ঝাঁড়ে। ছুটতে ছুটতে কাঁটাতারের বিশাল বেড়া ডিঙ্গিয়ে রেললাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। মনে মনে ভাবতো, কোনপ্রকারে রেলগাড়িতে একবার উঠতে পারলে বহু দূর-দূরান্তে পৌঁছে যেতে পারবে। দেশ-বিদেশ দেখতে পারবে। ঘুরতে পারবে। কেউ থাকবে না ওকে বাঁধা দেবার। মনের সাধ মিটিয়ে রেলগাড়িতে চড়তে পারবে।
তখন চৈত্র মাস। প্রায় প্রতিদিনই কাল-বৈশাখীর ঝড় ওঠে। সেদিনও দূপুর থেকে শুরু হয় গুড়–ম গুড়–ম মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। সেই সঙ্গে তুফানি পবন আর মরা কান্নার মতো বাতাসের একটানা গোঙানী। সে একেবারে প্রলয়ঙ্করী বেগে গাছেরডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে ছুটে চলে দিগি¦দিকে। তারপরই শুরু হয় বৃষ্টি। সে একেবারে মুসলধারে বৃষ্টি। যেন আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি। ফলে অনিবার্য কারণবশতঃ সেদিন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেলগাড়ি থেমে গিয়েছিল। কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য! কূয়াশার মতো ধোঁয়াটে আবরণে ছেয়ে গিয়ে চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। রাজ্যের হাঁস-মুরগী, পশু-পাখী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীই তার নিজের প্রাণ বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছিল। এমতবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই মরিয়া হয়ে উর্দ্ধঃশ্বাসে ঝন্টু ছুটে যাচ্ছিল রেলগাড়িতে উঠবে বলে। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খন্ডাবে কে! হঠাৎ বেকায়দায় পা শ্লীপ্ করে কাদার গভীরে আঁটকে যেতেই ঝন্টু হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁটাতারের ওপর।
সাধারণতঃ বিপদকালেই মানুষ হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। দিশা হারিয়ে ফ্যালে। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, মস্তিস্ক কাজ করে না। বুদ্ধিভ্রষ্ঠ হয়ে পড়ে। ঝন্টু তো অবুঝ, অবোধ বালক। তুলনামূলকভাবে তৎকালীন ছেলেমেয়েরা একবিংশ শতাব্দির ছেলেমেয়েদের মতো এমন ব্রিলিয়ান্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট ছিল না। সেল্ফ প্রটেকশন তো দূর এহেন দুর্যোগ দুরবস্থায় বিপদ অবশ্যম্ভাবী, তা ওর মস্তিস্কেই তখন উদয় হয়নি। কাঁটাতারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্যালে। আচমকা চোখদু’টোয় গুরুতরো আঘাতে ঘায়েল হয়ে কখন যে সেন্সলেস অবস্থায় রেললাইনের ধারে পড়েছিল, কেউ জানে না। তখন সেল ফোনের রেওয়াজও ছিল না যে প্রভারানী দেবী ফোন করে ছেলের খোঁজ নেবেন। উনি ভেবেই নিয়েছিলেন,-প্রবল বর্ষণে ঝন্টু আঁটকে গিয়েছে। এসে পড়বে ক্ষণ!
কিন্তু কোথায় ঝন্টু! কোনো পাত্তা নেই ওর। সময় যতো বাড়তে থাকে নানারকম দুঃশ্চিন্তা-ভাবনায় প্রভারানী দেবী অস্থির হয়ে ওঠেন। এমন দুর্যোগের মধ্যে ছেলেটা গেল কোথায়?
কিন্তু এ আর নতুন কি! সাংঘাতিক দুঃসাহসী ছেলে ঝন্টু। ওকে যে কোণ্ ধাতূ দিয়ে বিধাতা গড়েছিলেন, ডর ভয় বলতে কিছুই ছিল না শরীরে। একেবারে বাঘের কলিজা ওর। কী শীতকাল, কী বর্ষাকাল, সন্ধ্যে সাতটার আগে কোনদিন ওর টিকি পাওয়া যায় না। কিন্তু সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে সেই কখন! সাতটা বাজতেই ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। ঝন্টু তখনও নিখোঁজ, বেপাত্তা।
ততক্ষণে পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়। শুরু হয় ভাগ-দৌড়। উদ্বেগ-উ™£ান্ত ঝন্টুর মাতা-পিতা, বড় দিদিরা সবাই বিচলিত হয়ে পড়ে। তখন বিদ্যুৎ ছিলো না পাড়ায়। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। তা উপেক্ষা করেই এক হাতে ছাতা, আরেক হাতে হ্যারিকেন নিয়ে পাড়ার লোকজন সবাই খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। সবাই সবাইকে জিজ্ঞ্যেস করে,-‘ঝন্টুকে দেখেছ কোথাও? কোথায় গ্যাছে ও’ তোমরা কেউ জানো? ওকে কোত্থাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।’
একসময় থেমে যায় ঝড়-বৃষ্টি-তুফান। শিথিল হয়ে আসে প্রকৃতির উন্মাদনা। জলে থৈ থৈ করছে সারাপাড়া। গ্যাঁঙর গ্যাঁঙর করে ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। ঝন্টু তখনও নিখোঁজ। হাক ডাক দিয়ে হন্যে হয়ে তন্ন তন্ন করে ওকে খুঁজজে সবাই।
সেই সময় এক গোয়ালা দুধ দিতে আসতো পাড়ায়। সেদিন ফিরতি পথে হঠাৎ টর্চের আলোয় তার নজরে পড়ে, কে যেন মুখ থুবড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে রেললাইনের ধারে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাদাজলে মিশে চারপাশে কালো হয়ে আছে।
খবরটি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সারাপাড়ায়। আর শোনামাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পাড়ার যুবক ছেলেরা। যারা কাঁধে চেপে ঝন্টুকে নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানে প্রায় মাসখানিক চিকিৎসাধীনে থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে ঝন্টু বাড়ি ফিরে এসেছিল ঠিকই কিন্তু চিরতরে হারিয়ে গেল ওর চোখের দৃষ্টিশক্তি।
সেইদিন থেকে পাড়ায় উৎপাত উপদ্রপ, হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামিচি সব বন্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের আনন্দ-কোলাহল, হাসি-গুঞ্জরণ। আর ঝন্টু বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে বন্দি হয়ে পড়ে রইলো বাড়ির চার-দেওয়ালের বদ্ধ ঘরের ভিতর। কিছুতেই ভাবতে পারতাম না, ঝন্টু অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। ও’ একা কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু দিন কারো জন্য থেমে থাকে না। সময়ও কারো জন্য অপেক্ষা করে না। ঘড়ির কাঁটা ধরে সে তার নিজস্ব গতীতে দিবানিশি এগিয়ে চলে।
অগত্যা, বুকের গহীনে অদৃশ্য এক যন্ত্রণা পুষে রেখে কৈশোরের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলাম। মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে। তারপর কত ঝড়-তুফান এলো আর গেল, ঝন্টুদের আমবাগানে আমরা কেউ আর আম কুড়োতে যেতাম না। গাছের আম গাছতলাতেই পড়ে শুকিয়ে যেতো। কখনো পোঁচে গোলে দুর্গন্ধ বের হতো। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তো দূর, আমবাগানেই আর ঢুকতেন না ঝন্টু মাতা প্রভারানী দেবী। ফিরেও তাকাতেন না কখনো। এভাবে দীর্ঘদিনের নোংরা আবর্জনা জমতে জমতে একসময় গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। যেখানে রাজ্যের সাপ-ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় সব বাসা বেঁধেছিল। মনেই হোত না সেখানে মানুষজন বসবাস করে।
কিন্তু মানুষের জীবন নদীর প্রবাহ সদা চঞ্চল, বহমান। কখনো এক জায়গায় স্থীর থাকে না। জোয়ার ভাটার টানে কখন কোন্ মোহনার দিকে ধাবিত হয়, তা কেউ বলতে পারে না। তদ্রুপ কালের বিবর্তনে ঝন্টুরা জায়গা জমি বেচে দিয়ে আমাদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্রে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তারপর কখনো আর ওর সাথে যোগাযোগ হয়নি। দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।
আমার আজও অস্পষ্ট মনে পড়ে, চোখে কালো চশমা পড়ে ঝন্টু যেদিন হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। সেদিন ঝন্টুকে আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম। কী আনন্দ -কোলাহল আমাদের। প্রতিটি মুদিদোকানে হালখাতা হচ্ছিল। মাইকে শ্রুতিমধুর বাংলা গান বাজজিল। সেদিন নতুন জামা-কাপড় পড়ে বাংলা নববর্ষকে স্বাগতম জানাতে আমরা নাচে, গানে, সুর ও ছন্দের তালে মেতে উঠে ছিলাম, বাঙালির আবহমানকালের চিরাচরিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আনন্দমেলায়।
কিন্তু দুঃখের দহনে, করুণ রোদনে সেদিন ঝন্টুর মায়ের বুকের পাঁজরখানা কিভাবে যে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, তা অপরিণত বয়সে আমরা কেউ একবারও ভেবে দেখিনি। অনুভূত হয়ে নি। আমাদের একবারও মনে হয়নি, কিভাবে ঝন্টুর দিন কাটবে, রাত পোহাবে। জীবনের এতখানি দীর্ঘ পথ কিভাবে অতিক্রম করবে! কী হবে ওর ভবিষ্যৎ! কোথায় ওর মঞ্জিল! কী হবে ওর পরিণাম!
ঝন্টু সারাদিন জানালার ধারে বসে থাকতো। নৈঃশব্দে কেউ গিয়ে দাঁড়ালে তার উষ্ণ নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে টের পেয়ে যেতো। কখনো নিঃশব্দে কাঁদতো। দুইহাতে চোখের জল মুছতো আর জিজ্ঞ্যেস করতো,-‘স্কুল ছুটি হয়ে গেছে? তোরা এখনো খেলতে যাসনি?’
কিন্তু ওকে যে কোন্ ভূতে পেয়েছিল, জীবনের এতবড় একটা সম্পদ চিরতরে হারিয়ে ওর এতটুকু দুঃখ ছিল না। অনুপাত অনুশোচনা ছিল না। সারাদিন মন্ত্রের মতো শুধু একটাই বুলি জপতো,-‘রেলগাড়িতে আমার আর চড়া হলো না রে! কোনদিন আর রেলগাড়িতে চড়া হবে না আমার!’
কিন্তু কতদিন! যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেও কী ঝন্টু একই স্বপ্ন দেখতো? নিশ্চয়ই নয়! কারণ যৌবনেই নারী -পুরুষ প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় সৃষ্টি হয়, একটি কাল্পনিক জগত, একটি নিজস্ব ভুবন। যেখানে অবিরল অবয়ব রূপের মহিমায় মনগড়া কোনো এক স্বপ্নপরী কিংবা পক্ষীরাজের আর্বিভাবে প্রতিটি মানুষের মনের মণিকোঠায় অতি সংগোপনে লালিত হয়, জীবনের পরম কাক্সিক্ষত স্বপ্ন, কামনা-বাসনা। যার অব্যক্ত আনন্দে শরীর এবং মনকে পুলকিত করে। পুলকে বিকশিত করে। আর তারই প্রভাবে মানুষ কত না আকাশকুসুম রচনা করে ভাবনার জাল বোনে। কতই না রঙ্গিন স্বপ্ন আঁকা শুরু করে তার দু’চোখের কোণে। রচনা করে এক অনবদ্য প্রেম-ভালোবাসার পান্ডুলিপি। যখন জীবনের একান্ত চাওয়া পাওয়াকেই সবচে’ বেশী গুরুত্ব দেয় পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতি।
কিন্তু ঝন্টুর বেলায় তা হয়তো সম্ভব হয় নি। কিম্বা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। হয়তো বা আদৌ ওর অন্তরে ভাবান্তরই হয় নি। দৃষ্টিহীনতার গ্লানিতেই ওর হৃদয়পটে এঁকে রাখা রঙ্গিন স্বপ্নগুলি অশ্রুজলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে সব মুছে গ্যাছে। হয়তো বা ওর গহীন অন্ধকার অনিশ্চিত জীবনে চলার পথে সহযাত্রী হয়ে কোনো এক মায়াবিনি বিদূষী নারী সহমর্মিতা হয়ে ওকে আলোর পথ দেখাতে স্বেচ্ছায় ওর হৃদয়দ্বারে এসে ধরা দিয়েছে, তা কে জানে!