৬৭৫ বার পড়া হয়েছে
তুলনামুলক সাহিত্যের আলোকে সাবিত্রীর কাব্যগ্রন্থ ‘কাব্যফুলেঃ
রুমা পারভীনারা (বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা, ভারত)
অনুবাদ সাহিত্য অনুধাবনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য পাঠ ও সেই সাহিত্য বিষয়ক
বিচার-বিশ্লেষণ করা তুলনামূলক সাহিত্যের অন্যতম ও প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জন জাতির প্রতি তথাকথিত প্রগতিশীল জাতির অযাচিত বৈষম্য এবং সেই সব পিছিয়ে পড়া জাতির দৈনন্দিন সংঘর্ষের যাপনগাঁথা অধ্যয়নে ও বিশ্লেষণেও দারুণ ভাবে আগ্রহী তুলনামূলক সাহিত্য। বলা বাহুল্য, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পরিকাঠামোয় নারী জাতি বরাবর শোষিত, নিষ্পেষিত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই নারীকে দলদাস বানিয়ে রাখার প্রয়াস করেছে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। রুদ্ধ দার, গৃহ বন্দি রেখে সমগ্র নারি জাতিকে আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে নির্বিচারে। কালে কালে যুগে যুগে ভাষা ও সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে এক জাতি অন্য জাতির থেকে আলাদা হলেও লিঙ্গ নির্ভর বৈষম্যের দিক থেকে প্রত্যেক জাতি ব্যবস্থাই একরকম। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নয়নের দিকে মানব সভ্যতার এক অত্যাধুনিক যাত্রার সময়কালেও নারী জাতি পরাধীনতার শিকলে আটকে। অবশ্য, যুগে যুগে নারীবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎরা নারীদের মুক্ত করার চেষ্টাও করেছেন অবিরত। ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকের দিকে মহারাষ্ট্রের সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতমা। মারাঠি ভাষায় তাঁর রচিত কবিতাগুলি লিঙ্গ নির্ভর বৈষম্যের নির্ভেজাল দলিল। জাতিভেদ প্রথার মত সামাজিক সমস্যা, জাতিভেদ জনিত দাসত্ব থেকে মুক্তি, শিক্ষা, ঐতিহাসিক সত্যতা ও সচেতনতা তাঁর কাব্য চর্চার মূল উপজীব্য। তাঁর কাব্য চর্চায় ফুটে উঠেছে বর্ণাশ্রম নির্ভর জাতিভেদের মর্মন্তুদ চিত্র। এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সাবিত্রীবাই ফুলের ‘কাব্যফুলে’ গ্রন্থটি নির্বাচিত হয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্যের আলোকে কাব্যগ্রন্থে উল্যেখিত কবিতা গুলির স্বরূপ আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ নির্ভর, লিঙ্গ নির্ভর জাতি ব্যবস্থা গঠনের মনস্তাত্বিক দিক অনুধাবন করতে আগ্রহী এই প্রবন্ধে। অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার একটি জাতিকে শৈবালধামের মত আটকে রাখে। ফলে সেই জাতির অগ্রগতির দিকে এক অদম্য যাত্রা ক্ষুণ্ন হয় এবং সেই জাতিটি অচিরেই সমাজধারার মূল গতি প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাবিত্রীবাই ফুলের পূর্ব উল্লেখিত কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতাতেও ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত কুসংস্কারের চালচিত্র যা নারীবিদ্বেষ মূলক ঘটনার মতই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য দারুণ ভাবে দাবি রাখে। এই প্রবন্ধে তাই সাবিত্রী বাই ফুলের কবিতায় ফুটে ওঠা নারীবিদ্বেষ মূলক ভাবনা পোষণে কুসংস্কারের ভূমিকা ও স্বরূপ আলোচনা করে নারী অনগ্রসরে কুসংস্কারের ভূমিকা অধ্যয়নের চেষ্টা করা হবে।

সাবিত্রীবাই ফুলের “কাব্যফুলে” কাব্যের স্বরূপ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তৎকালীন সময়ের বাস্তবচিত্রে নারীঃ
তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত ছিল বহু অসামাজিক বিধি নীতির গাঁথুনি মালা দিয়ে।যেটার দ্বারা সেই সমাজের নারী শ্রেণীকে ভীষণভাবে পর্যুদস্তহতে হয়েছিল সামাজিক জীবন যাপনে। নারীদেরকে সামাজিক সংস্কৃতি থেকে সব সময় দেখা হতো এক বৈষম্যের আলোকে।কিন্তু যদিও বর্তমানের গতির নিরিখে সমাজ যথেষ্ট শিক্ষিত,রুচিশীল হলেও নারীকে আজও সেই দলদাসের মতোই ভাবা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে।বস্তুত নারী ছিল সর্বার্থেই পুরুষের নিপীড়ণের স্মীকার।উনুন সামলানো আর শিশুপালনই তাদের জীবনের এক বদ্ধ গণ্ডি ছিল। ঘরের কোণে আবদ্ধতার মধ্যেই তাদের জীবনযাপন করতে হতো। নারীর জন্য বরাদ্দ ছিল সীমাহীন অত্যাচার,তাদের শিক্ষা না দেওয়া, তাদের নিয়ে জুয়া খেলা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, বিধবাদের মস্তক-মুণ্ডন,জাতিভেদ জনিত নিষ্ঠুর অত্যাচার সবই ছিল নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর প্রয়োগ করারসমাজমান্য অধিকার। চোখে জল, বুকে মাতৃস্তন্য নিয়ে অবলা নারীর গোটা জীবনের মানে ছিল এক অন্ধকার কারাগারের মধ্যে কয়েকটি বছর পশুর মত জীবন যাপনের রোজনামচা। তেমনই উপমহাদেশের প্রান্তীয় বর্গে মহারাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থাও ব্যতিক্রমী কিছু ছিল না। তেমনই উপমহাদেশের প্রান্তীয় বর্গে মহারাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্হাও ব্যতিক্রমী কিছু ছিলনা। আর তারই নিরিখেই এক প্রতিবাদী সত্তার যেন আবির্ভাব হয় ধূমকেতুর মতো। তিনি তাঁর ‘কাব্যফুলে’ কবিতার প্রতিটি লাইনের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার চালচিত্র চিত্রাঙ্ককন করে দিয়েছেন। যেখানে আছে এই নির্মম ভাবে অত্যাচারিত ব্রাহ্মণ সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদের চাবুক।আছে নারীদেরকে নিজস্ব সত্ত্বা বুঝে নেওয়ার মূলমন্ত্র।উনবিংশ শতকের নারীবাদের ইতিহাসে নারীদেরকে আইনি অসমতা দিয়ে যেমন দমিয়ে রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনই তা পরিবর্তনের জন্য সাবিত্রীর কাব্যগ্রন্হ ‘কাব্যফুলে’ এর মধ্যে এক জায়গায় মনুর লেখা ‘মনুস্মৃতি’ তে নারীদের নিয়ে লেখার বিরুদ্ধে তাঁর তির্যক কটাক্ষ —
“মনু বলেন,
যারা মাঠে কাজ করে, আর লাঙল চালায়
মনু বলেন তারা ভোঁতা প্রকৃতির—
বস্তুত ব্রাহ্মণদের জন্য এটি নির্দিষ্ট!
মনুস্মৃতি বলে,মাঠে শ্রম দিওনা।”
এখানে মনুর এই উপদেশের সত্যতা নিয়ে সাবিত্রী
যথেষ্ট সন্দিহান। তিনি জানেন শূদ্রেরা আর অতিশূদ্রেরা
পরিশ্রম করে ফসল ফলালে নিশ্চিত তারা ধনী হয়ে
যাবে।
সাবিত্রীবাই ফুলে নারীবাদী সমাজের করুণ দৃশ্য একীভূত হয়ে বুঝেছিলেন নিরক্ষরতা ও শিক্ষাই মানুষকে বেঁধে রাখে বিভিন্ন আচার ঐতিহ্যের শেকলে।তেমনি বিভিন্ন কুসংস্কার, জ্যোতিষশাস্ত্র, হস্তরেখার মতো সমাজ শ্লেষের স্বীকারগ্রস্ত নারীর জীবন দূর্বিষহ ঠেকেছিল। এই কুসংস্কার মিশ্রিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে। তিনি এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নিন্দার বাণী উগরে দিয়েছেন তাঁর “কাব্যফুলে” নামক কাব্যগ্রন্থের কবিতাতে—
মূর্খেরা বিশ্বাস রাখে জ্যোতিষ শাস্ত্রে—
পঞ্চাঙ্গ আর হস্তরেখায়—
নিজেকে হারায় স্বর্গ-নরকের কল্পনায়।
পশুর জীবনেও নেই এমন স্থান।
যখন স্ত্রী দেয় শ্রম, নির্লজ্জ স্বামী করে আহার।
এমন পশুর যখন একটিও নেই—
এদের তাহলে কি করে বলে মানুষ!
তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্ন কুসংস্কার এর মধ্যে আটকে থাকলেও তিনি তাঁর কবিতায় স্মরণ করে গেছেন সমাজের দীপ্তি ধারী মহীয়সী নারীদেরকে। তাঁর কাব্যতে সেই দীপ্তি ধারী মহীয়সী নারীরা যেমন বীরাঙ্গনা, সাহসিনী, মারাঠা রানী তারাবাঈ স্বামীর মৃত্যুর পর দক্ষ হতে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। মোগল সম্রাট আগ্রাসনের হাত থেকে মোকাবেলা করে, যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে, রাজ্যভারের দায়িত্ব সামলেছেন।আর এজন্যই তিনি বারবার নারী শক্ক্তির কথাটাকে তুলে ধরে সমাজের কোণে আবদ্ধ থাকা নারীদেরকে পথে নামার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন। তিনি সে সময় কালে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের পাশাপাশি সূদ্র নারীদেরকে বেশি চিহ্নিত করেছেন। তিনি ধর্মীয় প্রথার জালে আবদ্ধ হয়ে থাকাকে কঠোরভাবে উপহাস করতে ছাড়েননি। ফলত তিনি তাঁর কাব্যে সেই কারণেই বলেছেন—
“তেলে চুবিয়ে রাখা পাথরের
সামনে দাঁড় করিয়ে
বোঝানো হয় সূদ্রকে
এই হল দেবতা।
কিন্তু আসলে সেটি ছিল
শুধুই পাথর।
সাবিত্রী ছিলেন সব ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। পুত্র পাবার আশায় দেবতার উপাসনারত মানুষকে তিনি বারে বারে বিদ্ধ করে বলেছেন এভাবে পাথর দেবতার পূজো করে যদি সন্তান পাওয়া যেত তাহলে নর-নারীর বিবাহ হয় কেন?
সমাজের অন্যায়, নারী, নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি বঞ্চনার বিষয় যেমন সাবিত্রীর তীক্ষ্ণ নজর এড়ায়নি, তেমনই প্রকৃতির অফুরান মাধুর্য বারেবারে তাকে মুগ্ধ, আবিষ্ট করেছে। তাঁর অনেক কবিতায় প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের ফুল অথবা প্রজাপতির বর্ণনা রয়েছে। ” হলুদ চাঁপা” শিরোনামের কবিতায় তিনি এভাবেই শিক্ষিত সমাজের শিক্ষিত হয়ে ওঠা নারীদেরকে তুলনা করেছেন বলেছেন —
হলুদের রং এর মত হলুদ চম্পা
ফুটে আছে বাগানে
হৃদয়ের গভীরে সে
পেয়ে গেছে স্হান।
সাবিত্রীবাই তাঁর গীতিকবিতায় নারীদের নিয়ে
বলেছেন—
” বাঁচা আর আত্মসম্মানের জন্য
যাও তবে স্কুলে,
শিক্ষা সে যে নর-নারীর আসল রত্ন,
যাও তবে এখনই স্কুলে।”
উনবিংশ শতকের নারীবাদের ইতিহাসে
নারীদেরকে আইনি অসমতা দিয়ে বাল্য বিবাহের
ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো।ঔপনিবেশিক শাসনকালে
ধর্মীয় হস্তক্ষেপের স্বীকার হয়ে অবিবাহিত নারীদের
উপর অকথ্য, অমানবিক অত্যাচার করা হতো। এই
অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু সমাজে মেয়েদের রক্ষা
করার জন্য জন্ম থেকেই বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল
এবং উনিশ শতকের পরবর্তী সময় থেকে এই
বাল্যবিবাহ ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত জায়গায়
প্রচলিত হয়ে যায়।
প্রাচীন ও মধ্যযুগের সময়কালে সমাজে গোড়া
হিন্দুদের দাসত্বের কারণ ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির
স্মীকার হয়ে বালিকাদের বয়ঃসন্ধির আগেই বিবাহ
দেওয়া হত। এই বাল্যবিবাহের কারণ গুলির মধ্যে
প্রধান হয়ে উঠেছিল দারিদ্র্যতা, যৌতুক, সামাজিক
প্রথা, বাল্যবিবাহ সমর্থনকারী আইন, ধর্মীয় ও
সামাজিক চাপ, অঞ্চল ভিত্তিক রীতি নীতি, অবিবাহিত
থাকার শঙ্কা,নিরক্ষরতা ও মেয়েদের উপার্জনে অক্ষম
ভাবা। বেশিরভাগ ধর্মেই এই বাল্যবিবাহ কে সমর্থন
করে। উনিশ শতকের পরবর্তী সময় থেকেই এই
বাল্যবিবাহ ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত জায়গায়
প্রচলিত হয়ে যায়। ফলে নারীদের অশিক্ষার অন্ধকারে
নিমজ্জিত করে রাখা হয় এবং বিভিন্ন কুসংস্কারে
আবদ্ধ করে রাখা হতো। আর এরই প্রতিবাদ স্বরুপ
ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে নিহিত মহারাষ্ট্রের এক
প্রতিবাদী নারী সাবিত্রীবাই ফুলে তাঁর ‘কাব্যফুলে’
কাব্যের বিভিন্ন কবিতাতে এই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে
সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ হেনেছেন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ
করে বালিকাদের শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা
করেছেন—
“প্রথম কাজটি পঠন পাঠন
তারপরে আছে গৃহকর্ম।
পাঠ নেওয়ার আগে
বাসস্থানটি করো পরিপাটি
তারপরে চলে যাও স্কুলে।”
সতীদাহ প্রথা তৎকালীন সময়ে বিশেষ
করে হিন্দু ব্রহ্মণ্য সমাজে এক ভয়ঙ্কর বিধি ছিল। এই
সতীদাহ প্রথা বা বিধবা বলির অন্ত্যোষ্টিক্রয়ার জন্য
চিতার উপর শুয়ে নিজেকে আত্মাহুতি দিতে হতো।
থাপার সতীদাহ প্রথার উত্থানের কারণ হিসাবে
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধস্তনতা, আত্মীয়তার
ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নারী যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণকে
ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এই নৃশংস সতীদাহের বিধিতে
অনেক নারীই মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার হলে তাকে
জোর করে স্বামীর চিতাতে শুইয়ে দেওয়া হতো। এই
সতীদাহ প্রথা নিয়ে ঐতিহাসিক রাল্ফ ফিচ ১৫৯১ সালে
উল্লেখ করেছেন –
“স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীকে তার সাথে
পুড়িয়ে ফেলা হয়, যদি সে বেঁচে থাকে, তবে
তার মাথা ন্যাড়া করা হয় এবং তার পরে তার
কোন হিসাব নেওয়া হয় না।”
সতীদাহ প্রথার উত্থান গুপ্ত যুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে
ঔপনিবেশিক যুগকে ছুঁয়ে গেছে। উনিশ শতকের
কালেও দেখা যাচ্ছে এই সতীদাহ প্রথা ভয়ঙ্কর রূপ
ধারণ করে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। কিন্তু এই সতীদাহ
প্রথা থেকে বাঁচিয়ে বিধবা নারীদেরকে পুনরায় বিবাহের
ব্যবস্থা করা হতো। অথর্ব বেদে বিবাহ সম্পর্কে বলা
আছে-
“ইয়ং নারী পতি লোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্ব্য
মর্ন্ত্য প্রেতম। ধর্মং পুরাণমনু পালয়ন্তী তস্মৈ
প্রজাং দ্রবিণাং চেহ ধেহি।”
উনবিংশ শতকের কালে বিধবাদের পুনরায়
বিবাহের ব্যবস্থা অর্থাৎ বিধবা বিবাহ দিয়ে তাদের
সামাজিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন
বিদ্যাসাগর। পাশাপাশি সাবিত্রীবাই ফুলে এই
বিধবাবিবাহের মাধ্যমে নারীদের বাঁচানো থেকে শুরু
করে তাদের সমাজে ধর্ষণ এবং বিভিন্ন কুসংস্কারের
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি নিজেই একটি আশ্রম
খুলে দিয়েছিলেন। তা তাঁর কাব্যের “উঠুন, শিখুন এবং
অভিনয় করুন” কবিতার মাধ্যমে তিনি নারী জাতিকে
বলেছেন —
দুর্বল ও নির্যাতিতা!
উঠ আমার ভাই দাসত্বের
জীবন থেকে বেরিয়ে আসুন।
মনু অনুসারী পেশওয়ারা মারা গেছে এবং চলে
গেছে,
হে ব্রাহ্মণ, তুমি বিচলিত হও না।”৯
তাঁর কাব্য থেকে জানা গেছে তিনি সমাজের মহিলাদের
বিশেষ করে দলিত শ্রেণীর নারীদের শিক্ষার জন্য
বারবার আহ্বান করেছেন। তিনি একজন দলিত হয়ে
দলিত শ্রেণীর যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত আর তাঁরই কবিতায়
দলিত,সাধারণ নারীদেরকে শিক্ষার কথা বলেছেন।
পাশাপাশি তাদের শিক্ষিত হয়ে সাবলম্বী হয়ে ওঠার
কথা বলেছেন “Go-Get Education” —
” হও আত্মনির্ভর, হও পরিশ্রমী, কাজ করো,
জ্ঞান অর্জন করো, জ্ঞান ও ধন….
তাই পাঠ নাও, ভেঙ্গে দাও যাতের শেকল,
দ্রুত ছুড়ে ফেলো যতসব ব্রাহ্মণদের পুঁথি। “
তাঁর কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তৎকালীন
সমাজে ব্রাহ্মণ্য বাড়াবাড়ি। তাঁরা বিভিন্ন জাতপাতকে
নির্ধারণ করে এবং নিচু শ্রেণীর জাত শূদ্র ও
অতিশূদ্রদেরকে বিভিন্নভাবে কুক্ষিত করে রাখার চেষ্টা
করত। তাদেরকে ঘৃণা করতো। নারীবাদী দিক থেকেও
সমাজের নারীদের বিভিন্নভাবে ভোগ্যপণ্য হিসেবে
ব্যবহার করতো। এই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মানুষ শুধু
এটা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক,
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের অধিকার কায়েম করে
রেখেছেন আর তাদের ঘৃণার আঁচে নারীরাও কবলিত
হতো। তিনি তাঁর “কাব্যফুলে” কাব্যের কবিতায়
জাতপাতের বিদ্বেষ নিয়েই তির্যক প্রসঙ্গ টেনেছেন —
শূদ্র আর অতিশূদ্রেরা
অজ্ঞতায় যারা পশ্চাদপদ
হয়ে গেছে ভিখিরি
দেবতা,ব্রহ্মণ আর ধর্মের পূজার্চনায়।।
সাবিত্রী নিজের জীবন দিয়েই অনুভব করেছেন সমাজে
নারী আর নিম্নবর্গের মানুষের শোচনীয় দুরবস্থা। আর
সমাজে তাদের যথার্থ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার একমাত্র
কারণ তাদের নিরক্ষরতা।এই নিরক্ষরতা থাকার কারণ
ব্রাহ্মণ্য সমাজ। তৎকালীন সমাজের উঁচু মানুষদের
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু নিম্নবর্গ, শূদ্র শ্রেণীর
মানুষদের যেন কোনও অধিকার নেই। অধিকার নেই
সমাজের সুকাজে অংশগ্রহণে।সেকারণেই এর বিরুদ্ধে
গর্জে ওঠা। সাবিত্রীর কন্ঠে গড়ে ওঠে একটা ভয়ঙ্কর
মহীরুহ। তিনি কঠোর হাতে দমন করার জন্য তাঁর
কবিতায় কলমকে শানিত কুঠার বানিয়েছেন। এ হেন
উদ্যামতা তৎকালীন সমাজের মুখে কুলুপ এঁটে দেয়।
তিনি কবিতায় বলেছেন—
“নাম তার অজ্ঞানতা —
দৃঢ়তায় ধরে তাকে, করো আঘাত
ফেলো সরিয়ে জীবনের—
সীমানা থেকে ।।”
পরিশেষে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কালের
অর্থাৎ ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে প্রথম দার্শনিক নারীবাদী
ছিলেন সাবিত্রীবাই ফুলে। আশৈশব সাহসিনী
সাবিত্রীবাই ফুলে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার
বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেই সময়ের পটভূমিতে
দাঁড়িয়ে পিছিয়ে পড়া সমাজের মেয়েদের শিক্ষার জন্য
যেমন মায়ের মমতা দিয়ে সামগ্রিক দায়ভার কাঁধে তুলে
নিয়েছেন। তেমনই তিনি সেই শিক্ষা সমাজকে দিতে
চেয়েছেন যে শিক্ষা তাদের শৃঙ্খল মুক্তির পথ দেখাতে
পারে। সর্বার্থেই ব্যতিক্রমী নারী সাবিত্রীবাই ফুলে
ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম মহিলা যিনি নিজ
কণ্ঠস্বর দিয়ে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন “কাব্যফুলে”।
ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রথম এই নারী কবি
সাবিত্রীবাই ফুলের রচিত “কাব্যফুলে” কাব্য গ্রন্থের মধ্যে
দিয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার চিত্র সুন্দরভাবে
চিত্রায়িত হয়ে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার চোখে
আঙুল দিয়ে দিয়েছেন।






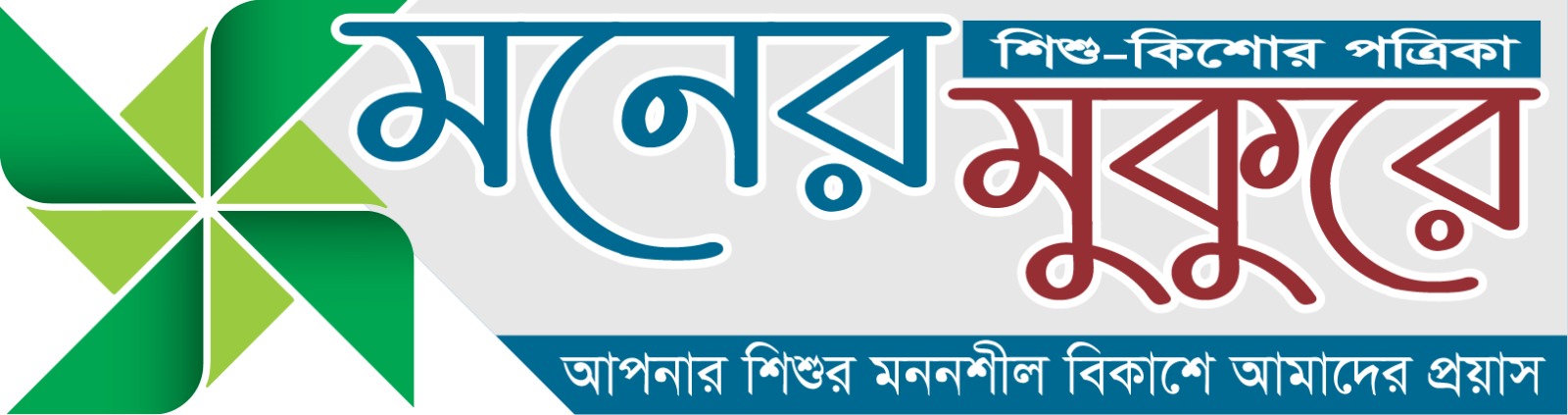
১ Comment
congratulations