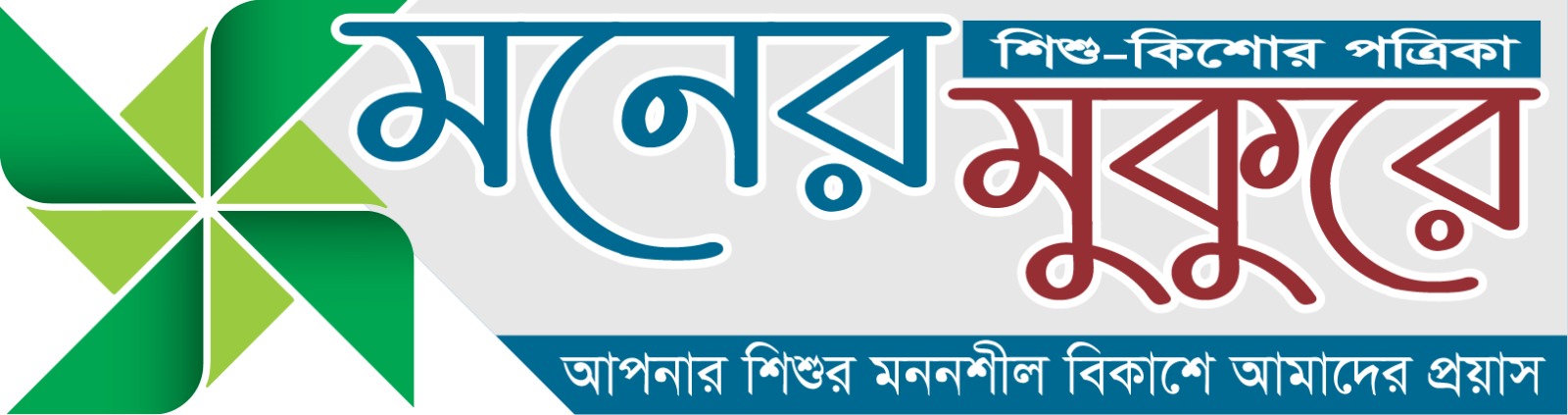৪২৭ বার পড়া হয়েছে
অন্তর্ধানের ৫০ বছর : উদ্ধার নাটকীয়তায় চলচ্চিত্রকার
জহির রায়হানের জীবনে ‘বেহুলা-সুচন্দা বনাম মনসা-সুমিতা’র অভিশাপ! # কবিতার আরশিতে অন্তর্ধানে’র কলঙ্ক…
সালেম সুলেরী
১৯৮৬ সালে আমার সাক্ষাৎকার নিলো দু’জন প্রতিশ্রতিশীল তরুণ। অথচ আমি নিজেই তখন এক তরুণ লেখক-সাংবাদিক। সাপ্তাহিক পরিবর্তন-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। যাঁরা সাক্ষাৎকার নিলো তাঁদের এড়াতে পারিনি। কারণ তাঁদের বাবা কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব জহির রায়হান। তাঁদের মা খ্যাতিমান চিত্রনায়িকা সুমিতা দেবী। আর তাঁরা দু’জন হলো– অনল রায়হান, বিপুল রায়হান।
‘মিডিয়ায় তারুণ্যের শক্তি’ বিষয়ক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করছিলো। তাঁরা দু’জন তখন একটি মুূ্দ্রণ-মিডিয়ায় জড়িত। জানালো– মিনার মাহমুদ ও আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। মিনার তখন সাপ্তাহিক বিচিন্তা’র সম্পাদক-প্রকাশক। তসলিমা নাসরিনের তৃতীয় স্বামী তখনও হয়নি। আর আমার বিয়ে-সংসার– আরো ৬ বছর পর।
সাক্ষাৎকারের পর ছিলো নির্ভেজাল এক আড্ডাপর্ব। ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক সাঈদ বারী, জসিমউদ্দিন, সালেহ আতাহারও। জহির রায়হান-এর সন্তানদ্বয়কে বেশ মেধাবী মনে হলো। প্রশ্ন করলাম– জীবনের শুরুতে তোমরা সাংবাদিকতায় কেনো? তাঁদের স্পষ্ট উত্তর– বাবাও তো তাই করেছিলেন। জহির রায়হানের অন্তর্ধান ও উদ্ধারের প্রসঙ্গটিও তুললাম। ১৫ বছরের পুরনো বিষয়টিতে তাঁরা আগ্রহ দেখালোনা না। বললো– রাষ্ট্রকে উদ্যোগী করা যায়নি, এখন কে করবে? আবার প্রশ্ন– তোমাদের পরিবার থেকেও তো কোন চাপ নেই!
অনল-বিপুল চাপা কন্ঠে জবাব দিলো। বললো, মা একসময় চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। বরং আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিরা ভিন্ন কথা বলেছেন। আপনারা তো জানেন– বাবা সুচন্দা আন্টিকে বিয়ে করেছিলেন। ওনারা তখন সেই প্রসঙ্গটিই তুলতেন। বলতেন, শেষবউ নায়িকা সুচন্দা কিছু করুক। কিন্তু উনি কি আন্দোলন করবেন। উনিতো আরেকটি সংসার পেতে ভিন্নজগতে আছেন। আমরা এটা বুঝি– বাবা আর পৃথিবীতে নেই। কিন্তু উনিওতো দেশটি আনার জন্যে কতো খাটলেন। সেই দেশের নেতারা ওনার অনুসন্ধানে কিছুই করলো না।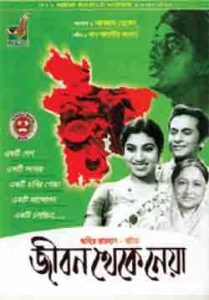
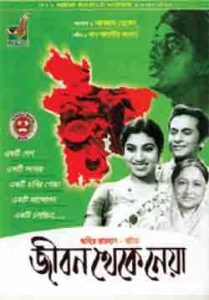
অনল-বিপুলের অনুযোগে ভারী হলো পরিবেশ। হালকা করার জন্যে নতুন কথা পাড়লাম। বললাম– আসলে ‘মনসা দেবী’র অভিশাপ লেগেছে। তোমার বাবা ‘বেহুলা’ ছবিটি বানিয়েছেন। তাতে রাজ্জাক নায়ক, মানে লখিন্দর। আর তোমাদের ছোট-মা সুচন্দা নায়িকা বেহুলা। অন্যদিকে তোমার মা সুমিতা দেবী ‘মনসা সাপের দেবী’। তিনিইতো অভিশাপ দিয়েছিলেন– বেহুলাকে সাপে কাটবে। বাসরঘরেই সাপে কাটবে শুনে লোহার ঘর বানালো। মনসা দেবী কামারকে ধরে নিশ্ছিদ্র ঘরে ফুটো করালো। শেষে সাপ ঢুকলো এবং লখিন্দরকে ছোবলও মারলো। তারপরতো বেহুলা ভেলায় ভাসালো সেই বিষদেহ। কবি তসলিমা নাসরিন সে বিষয়ে কবিতাও লিখেছে। –‘বেহুলা একাই ভাসিয়েছিলো ভেলা’, বুঝলে? অনেকে বলে– তোমার বাবার প্রতি মায়ের অভিশাপ ছিলো। প্রচারণা আছে– মনসা মানে সুমিতা দেবী’র অভিশাপেই এমনটি। মহামেধাবী জহির রায়হান অকালেই চলে গেলেন!
অনল-বিপুল বললো– না, তা মনে হয় না। মা তেমন জটিল মানুষই নন। তিনি সুচন্দা আন্টিকে মেনে নিয়েছিলেন। বাবার জন্যে মা এখনও নীরবে কাঁদেন। তবে, সেই সময়টায় কেঁদেছিলেন অবহেলা পেয়ে। আমরা শৈশবকাল থেকেই যেন এতিম, অসহায়। মানুষের জীবন কাহিনী নিয়ে শতো চলচ্চিত্র হয়। অথচ নির্মাতার ঘরের ভেতরেই কতো বিষাদভরা কাহিনী!
‘জীবন থেকে নেওয়া’ ছবির সফল নির্মাতা ছিলেন জহির রায়হান। নিজের জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন ১৯৭২-এর ৩০ জানুয়ারি। সহোদর শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। সহোদরকে জাতি আখ্যা দিয়েছে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী’ অভিধায়। কিন্তু একাত্তুরের বীর চিত্রযোদ্ধা জহির রায়হান কোনো আখ্যা পাননি। মিরপুরে বিহারী পল্লী অভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় চিরতরে হারালেন, তার নিশ্চিত তথ্য নেই। স্বাধীনতা অর্ধশতাব্দীকাল ছু’য়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার অকুতোভয় মেধা-যোদ্ধা জহির রায়হান যেন অনাহূত। অন্তর্ধানের রহস্য উদঘাটন নিয়ে কোন সক্রিয় কমিটি নেই। গোয়েন্দা তথ্য আহরণে নেওয়া হয়নি কার্যকরী পদক্ষেপ।
জহির রায়হান পেশাজীবন শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতা দিয়ে। পঞ্চাশের দশকে ‘যুগের আলো’ পত্রিকার মাধ্যমে। জাতিকে আলো প্রদানের কাজটিই বরাবর করেছেন। অথচ নিজের জীবন-উপান্ত নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত। হত্যাঘটনার কোন বিস্তারিত বা সত্যাশ্রয়ী ইতিহাস নেই। তিনিও যেন রহস্যে হারানো ‘নেতাজী সুভাষ বোস’। কিংবা একালের ট্রাজেডী ‘সাগর-রুনী, ইলিয়াস আলী’! বা ‘মৃত্যুরহস্যেরও মৃত্যুপ্রাপ্ত আরেক কাব্যপ্রয়াসী ‘মাহবুবুল হক শাকিল!’
জহির রায়হানের জন্ম ১৯৩৫-এর ১৯ আগস্ট। বৃহত্তর নোয়াখালির ফেনী জেলার মঞ্জুপুরে। পারিবারিক নাম ছিলো মোহাম্মদ জহিরউল্লাহ। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রথা মানতে নাম বদলান। দুই শব্দে তা আধুনিকীকরণ করেছিলেন। সেই সংশোধিত নামটিই সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে নীরব কিংবদন্তী।
জোড়া শব্দের জহির রায়হান জোড়া বিয়েও করেন। দুই বধুই তৎকালে খ্যাতিমান অভিনেত্রী। ১৯৬১ সালে– পরিবর্তিত নামের সুমিতা দেবী। ১৯৬৮ সালে কহিনূর বেগম সুচন্দা। চিত্রনায়িকা ববিতা ও চম্পার জ্যেষ্ঠ সহোদরা। জহির রায়হানের মাধ্যমেই পপি বা ববিতার চলচ্চিত্রাঙ্গনে স্বর্গপ্রবেশ। সিনেমাঙ্গনে জহির রায়হানের প্রবেশ–সহকারী পরিচালক হিসেবে। পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে– বাংলায় অনার্স। পরে উচ্চতর– পোস্ট গ্রাজুয়েট। ছবিপাড়ায় প্রথম পরিচালক হন ১৯৬৪ সালে। ‘কখনও আসেনি’ সাদাকালো ছবি দিয়ে। এরপর তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে গড়েন নতুন রেকর্ড। প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র বানান ‘সংগম’ শিরোনামে। তবে সর্বাধিক খ্যাতি পান ‘জীবন থেকে নেয়া’ মুক্তি দিয়ে।
কী ছিলো সেই অকুতোভয় অগ্নি-ছবিতে? মূলত বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম-অনুপ্রেরণা। জহির রায়হান ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে সমুখের সক্রিয় কর্মী। সেই সক্রিয়তার ছায়া যেন ছবিটিতে মূর্ত। কাজী নজরুলের ‘লাথি মার ভাঙরে তালা’র সার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। অসাধারণ অভিনয়শৈলী উপহার দিয়েছিলেন কুশীলবেরা। নটরাজ আনোয়ার হোসেন, নায়করাজ রাজ্জাক, বহুমাত্রিক খান আতা। ছিলেন রওশন জামিল, সুচন্দা, রোজী সামাদ, ববিতা, আলতাফও। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধকালে ছবিটি প্রদর্শিত হয় ভারতের কলকাতা’তেও। কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকারেরাও ছবিটি একঝলক দেখেন। অবিশ্বাস্য ভালো বলে মতামত দেন চিত্রগুরু ব্যক্তিত্ববৃন্দ। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা, ঋত্তিক ঘটক…। সবার মুখেই তখন প্রাণখোলা প্রশস্তি। সে সময়ে প্রদর্শিত ছবিটির পুরো আয় নিবেদিত হয় মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের সমূহ কল্যাণে, বিশেষ তহবিলে। ‘লেট দেয়ার বি লাইট’-এর কাজ অসমাপ্ত ছিলো। এরপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র ‘স্টপ জেনোসাইড’ । পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার বনাম
বাঙালি জাতির আর্তচিৎকার। যুদ্ধে বাঙালির প্রয়োজন দ্রুত অগ্রবর্তিতার। ইংরেজি ডাবিং সম্পন্ন এই ছবিটি বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ‘মৈত্রীবন্ধু’ ইন্দিরা গান্ধীও তা দেখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতার বিবরণ দেখে মুগ্ধ হন।
পেশাচর্চায় শুধুই কি চকমকে সিনেজগত? তার আগে জহির রায়হান প্রথম কাতারের কথাসাহিত্যিক। একাধিক কালজয়ী লেখার অদম্য মহীরূহ। ‘আরেক ফাল্গুন, শেষ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী। হাজার বছর ধরে’– বহুপঠিত কথাসাহিত্য। আমাদের সদ্য-তারুণ্যে সে এক মননগেলা গল্পগ্রাস।
সহোদর শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক। ঐ পরিবারেরই সুগৃহিনী অধ্যাপিকা পান্না কায়সার। কন্যা অভিনেত্রী-সংগঠক শমি কায়সার। পুত্র প্রকৌশলী অমিতাভ কায়সার। আরেক নিকটাত্মীয় লেখক-সংগঠক শাহরিয়ার কবির। অর্থাৎ কমবেশি সবাই সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত। জহির রায়হানের দুই সন্তানও সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডে নিবেদিত। অনল রায়হান, বিপুল রায়হানের জন্ম সুমিতা দেবীর গর্ভে। জহির-সুচন্দা জুটির সন্তানের খবর মিডিয়ায় নেই। তবে ১৯৭২-এর বিধবা সুচন্দা পরে আবার ঘর বাঁধেন। সংস্কৃতিসেবী আলী আজগর স্বপনের তথ্যমতে– স্বামী মনু হোসেন।
৩০ জানুয়ারি এলেই সচেতন মহলে জহির রায়হান মূর্ত হন। ৯০-এর দশকে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। অগ্রজ লেখকের প্রতি অনুজের দায়িত্ববোধ থেকেই। শিরোনাম : ‘সাফল্যের অন্তর্ধান ও জহির রায়হান’। ‘গৃহযুদ্ধের চাষ’ নামক আমার একটি কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত। ২০০২-এ কবিতাটিকে ঘিরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগঠন ‘সোনারতরী’। বিটিভির ‘প্রবাসমেলা’ খ্যাত আবৃত্তিশিল্পী মামুন ইমতিয়াজ ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খ্যাতিমান লেখক-সাংবাদিক রাহাত খান। দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন সম্পাদক-কলামিস্ট তিনি। বলেছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানের রহস্যটি গভীরতর। হয়তো ভবিষ্যৎ পৃথিবী তা জানতে পারবে না। কিন্তু জহির রায়হানকে জানতে মানুষের আগ্রহ চিরায়ত হবে। তাতে কবি সুলেরীর এই কাব্যনিবেদনটি আজীবন সহায়তা দেবে। বক্তব্যে-দাবিতে এটি যেন উঁচুদরের সম্পাদকীয়ও হয়ে উঠেছে।
সাফল্যের অন্তর্ধান ও জহির রায়হান =
রাজনীতি তোমাকে পদক দেবো,
তুমি আমাকে সন্ধান দাও সত্যতার।
অসংখ্য মানুষ
তিনভাগ সমস্যার সাথে তোমার সংসার,
আমি আজ শুধু একজন মানুষকে চাই–
যিনি ‘হাজার বছর ধরে’ জন্মেছেন,
মৃত্যুও হয়েছে বলে ধারণা ধারণ করি,
তবে শেষ বিদায়ের দৃশ্যপট, কিছুই জানি না।
তিনিতো কিশোর নন, বোবা-কালা-কানা নন
যে নিখোঁজ সংবাদ ছাপা হবে,
তবুও কপাল পোড়া দেশের, জানুয়ারির ৩০ তারিখ
আমরা সবাই বোকা বনে যাই,
অসহায় চোখে দেখি কাগুজে শব্দের বাহাদুরি–
‘আজ সেই অন্তর্ধান দিবস’, আহারে
বারুদের ক্লান্তিসাল হে উনিশশত বাহাত্তর–
শমিত-শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যারহস্য ঘাঁটতে গিয়ে
নিজেইতো রহস্যসাগরে ডুবচুপে ঘোরের শরীর!
আদতে জহির রায়হান এক অসমাপ্ত গল্পচিত্র!
মেধাবী জাহাজ যেন
লেখায়-রেখায়-দেখায় কি সিনেমায় কি প্রণোদনায়
বাংলায় শাশ্বত মধ্যবিত্ত, ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’–
হে ‘জীবন থেকে নেওয়া’ অপশাসনের প্রতিবাদী মুখ
ভাষাভঙ্গ ভূমি, স্বপ্নভঙ্গের সমুখে দাঁড়িয়েই
খুঁজেছিলো ‘আরেক ফাল্গুন,’
এবং বাঙালি কেবলই খোঁজে
আরেক জহির রায়হান, জ্বি– ‘লেট দেয়ার বি লাইট…’
প্রিয় রাজনীতি, শাসনের বাতিঘর,
আরেকবার আলোটা জ্বালো, ডুবুরী ডোবাও
বঙ্গোপসাগরে, উপকণ্ঠেই ডুবন্ত আজ-
সেই মানুষ টাইটানিক, গলন্ত জাহাজ,
তার সাথে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের ব্যথাভরা
স্বাধীনতার দলিল-দম্ভ, স্মৃতির লকেট,
তার ভেতরেই কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে আছে
একটি অমুক্ত অবিনাশী পাখির আপীল আর্তনাদ,
তার ঠোঁটে অবরুদ্ধ হয়ে আছে
তিনভাগ জল বাদে একভাগ ভূমি ইতিহাস,
আরো কিছু স্বাধীনতা, শামুক সভ্যতা, স্মৃতিলাশ !
প্রিয় রাজনীতি, ক্ষমতা দেখাও-
সেই অপহরণের– যে অপমৃত্যুর– সে অপলজ্জার
রহস্য না জেনে, শত্রু-মিত্র না বুঝেই
কিভাবে বাংলাদেশ নেবে মৃত্যুকোল,
কিভাবে গলবে জিজ্ঞাসার বিক্ষুব্ধ বরফ,
কিভাবেই বা বয়ে যায় সাফল্যের নড়বড়ে নদী!
আমি তার কবর চিনি না, শহীদ বেদীও না,
কোনো স্মৃতিপাত্র দেখিনা যেখানে
শ্রদ্ধাঞ্জলির তাবৎ বর্ষফুল মেলে ধরে
ক্ষমা ভিক্ষার সুবিধে নেবো।
এ ভাবেই ঋণ বাড়ে, দিন বাড়ে
সাফল্যও বেড়ে যায় অবকাঠামোর,
বাড়ে ব্যর্থতাই বড়ো জোর, শুধু গৌরব বাড়ে না,
পতাকা যেভাবে কাঁপে, সেভাবেই
শহিদী আত্মার দেহ– দুর্ভাগ্যের কাঁপন ছাড়ে না!
বেহুলা’র জলকান্না, লখিন্দরের কফিনবিষ
আমারই স্বাধীনতার মুক্ত ঘাড়ে না, ঘাড়ে না..।
থেকো না জহির রায়হান– অন্তর্ধানময় রহস্যপাড়ে না।