৪১১ বার পড়া হয়েছে
কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শতবর্ষ
(মোস্তফা তোফায়েল হোসেন)
২৫ মে ২০২১
এগারোই জৈষ্ঠ্য চৌদ্দ শ আটাইশ সাল।
কাজী নজরুল ইসলাম ‘বিদ্রোহী’ রচনা করেন ১৯২১-এ, যে-বছরে টি, এস, এলিয়ট রচনা করেন তাঁর কবিতা, ‘The Waste Land’। ১৯২১ সালেই প্রকাশিত, অপর শ্রেষ্ঠ কবিতাটির নাম ‘The Second Coming’, আইরিশ কবি ডব্লিউ, বি, ইয়েটস্ রচিত, যে কবিতায় পূর্বাচলে এক ‘আচানক, উদ্ভট জৈবিক শক্তি’র উদয় সম্পর্কে পূর্বাভাস উচ্চারিত হয়েছিল। এবার এদের শতবর্ষ।
‘বিদ্রোহী’ রচনার আগে কাজী নজরুল ইসলাম সমধর্মী গতিময়তার যে-কবিতাটি রচনা করেছিলেন, সেটি ‘আগমনী’। ‘আগমনী’র ছন্দ ও উচ্চারণভঙ্গিটিই প্রচণ্ড গতিশীলতার, ঝোড়ো চঞ্চল বেগে এগিয়ে চলার। কাজী সব্যসাচীর আবৃত্তিতে প্রতীতি আসে যে, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গুরুগুরু কম্পনে কথাগুলো ধেয়ে চলছে, যেমন করে ধেয়ে চলার আবেগ প্রকাশ করেছেন বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে’ এবং ইংল্যান্ডে পি, বি, শেলি তাঁর কবিতা ‘Ode to the West Wind’-এ। ঝোড়ো, বিরামহীন গতি কবিতার ভঙ্গিতে নিয়ে আসার অভীপ্সা থেকে শেলির এই কবিতাটিতে বারো পঙ্ক্তিবিশিষ্ট স্তবকগুলোর মাঝে কোনো full-stop বা বিরতিচিহ্ণ নেই, কমা ইত্যাদি বিরামচিহ্ণ আছে । নজরুল যেমন ‘বিদ্রোহী’তে গতিমাতম তাণ্ডব সৃষ্টিকল্পে দেবতা ‘নটরাজ’কে উপস্থাপন করেন, শেলিও তেমনই উপস্থাপন করেছিলেন ‘বনদেবী’র মত্তমাতাল আবহকে।১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিশেষ একজন দূতের আগমন ঘটে বলে উল্লেখ আছে, গত শুক্রবার প্রথম আলোর সাহিত্যপাতায়, সৈয়দ আজিজুল হকের প্রবন্ধে। আমি বইপত্র হাতড়ে, মস্কো থেকে কমিউনিস্ট নেতা এম, এন, রায়ের সেই দৃতের নাম পেলাম: ‘নলিনী গুপ্ত’। উনি কিছু বই ও পত্রিকা নিয়ে এসেছিলেন সেই সপ্তাহেই। খুবই সম্ভব যে সেই বইগুলোর মধ্যে ব্রিটিশরাজের উচ্ছেদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিষয়ক বই অন্তর্ভুক্ত ছিল। নজরুল এসব পড়েছেন ও প্রভাবিত হয়েছেন। ‘বিদ্রোহী’-তে যে ‘ভগবানে’র বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার অভিলাষ দেখি, সেই ভগবান ওই ব্রিটিশরাজ। এমন ভগবানের ধ্বংস কামনার অর্থ Jean Francoise Lyotard বর্ণিত পরবর্তীকালের চেতনা, যার নাম Grand Narrative ভেঙে দেওয়া। এটিই উত্তর-আধুনিক, উত্তর-উপনিবেশবাদী প্রবণতা। নজরুল যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পাঠ নিয়েছিলেন, এবং ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ‘ঘুর্ণন’- ‘চুর্ণন’ নির্মাণ প্রকল্পে এই মিশন ব্যক্ত করেছেন, তার দিকে আলোকপাত করেছেন প্রবীণ নজরুল গবেষক ও অনুবাদক মুহম্মদ নূরুল হুদা, তাঁর প্রকাশিত একাধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে। ড. গৌরাঙ্গ মোহান্ত’র ‘বিদ্রোহী’ নিয়ে ঋদ্ধ আলোচনা ‘ নজরুলের দ্রোহ প্রকৃতি ও শান্তিসূত্র’ শীর্ষক প্রবন্ধেও আমরা এই ‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে’র ইঙ্গিত পাই, যেখানে তিনি লেখেন, “তৃতীয় স্তবক(৪২-৫৩) পঙ্ক্তিতে উত্তম পুরুষের পরস্পরবিরোধী শক্তিধর দ্বৈতসত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে।” ড. গৌরাঙ্গ মোহান্তর এই প্রবন্ধটির শিরোনামেও একটি দ্বন্দ্ব উদ্ভূত সংশ্লেষ তথা শান্তির উল্লেখ আছে, যা নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার টেক্সটে হেগেল ও কার্ল মার্কস-এর বিখ্যাত সমাজতত্ত্বটির উপস্থিতিকে আভাসিত করেছে।
‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি উত্তর-আধুনিক ভাবধারার কবিতা, নৈরাজ্যপনা যে-রাজ্যের প্রধান রীতিনীতি। সীমানাহীনতা ও প্রান্তমুক্ততা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে উত্প্রেক্ষাজাত প্রতীকধর্মিতা। এই কবিতার নৈরাজ্যসুলভ প্রবণতার মধ্যে ‘খোদা’ ও ‘ভগবান’ঘটিত যেসব শৃঙ্খলাভঙ্গ আচরণ আছে, তা সবই প্রতীকী। ইংরেজ উপনিবেশবাদী শাসক এসব প্রতীকে অর্থায়িত। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে ইংরেজ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নাইট’ উপাধি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। কাজী নজরুল ইসলামের ‘নাইটহুড’ উপাধি ছিল না; তিনি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন তাঁর সকল নিয়ম-নিষ্ঠা ও সদাচরণের পরিভাষা। নাইজেরিয়া ও কেনিয়ায় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে ব্রিটিশ, যারা তখন পরম শক্তিমান। নজরুল তাদের আইনপ্রণেতা ‘বিধি’ বলে বিদ্রুপ ও ব্যাঙ্গ করেছেন মাত্র। ‘খোদা’ ও ‘ভগবান’ অভিধা দুটিও ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের চাবুক। বিচারহীনতাই যেসব আইনপ্রণেতাদের বৈশিষ্ট্য, তাদেরকে কথার কষাঘাত হানতেই নজরুল হয়েছেন ‘অনিয়ম, উশৃঙ্খল’। প্রতিবাদের ভাষাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করতে তিনি হয়েছেন ‘এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর।’ নটরাজ শিবের দুরন্ত, অফুরন্ত, দুর্বিনীত, দুর্দান্ত নৃত্যকর্মরত ভূমিকায় সচঞ্চল থাকেন তিনি ওই প্রতিবাদ প্রকাশ করার মানসেই। এখানেও প্রতীকের প্রয়োগ। বিপুল সংখ্যক উপমা ও উত্প্রেক্ষার ব্যবহার ঘটেছে কবিতাটিতে। ছন্দের যে মুক্ততা, তা-ও প্রতীকী। এখানে স্বরবৃত্ত আছে, মাত্রাবৃত্ত আছে, মাত্রাবৃত্ত মুক্ত্যক আছে। এক সংস্কৃতি থেকে আর এক সংস্কৃতিতে ‘ফিঙ দিয়ে দেই তিন দোল’ প্রবণতা আছে। কবি-প্রটাগোনিস্ট এখানে উন্মাদ, যিনি উন্মাদগ্রস্ততার ছলে ‘সব বাধ’ খুলে নেচে বেড়াবেন। কিন্তু তিনি উন্মাদ একটি বিশেষ লক্ষ্যে, যার নাম ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ। যেমন শেকসপিয়রের হ্যামলেট উন্মাদ একটি নির্দিষ্ট কোণ বরাবর: “I am mad, but mad in the North-North-West.” এবং, “There is method in his madness.”। তিনি তো নিপীড়িত জনগণ ও ভারতবাসীদেরকে গালি দেননি! নজরুলের এসব উশৃঙ্খল কথাবার্তা ও আচরণ একটি নির্মম সত্যের উন্মোচনকে সামনে নিয়ে।
‘বিদ্রোহী’ রচনার আগে নজরুল কোন কোন কবিতা ও গদ্য পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে-তালিকার ফর্দ তৈরি জরুরি নয়। আমি ধরে নিয়েছি যে আগ্রাসী পাঠক নজরুল ‘Song of Myself’ থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কবিতা ‘পরিচয়’ পর্যন্ত সবই পড়েছেন; কিন্তু কারো লেখা থেকেই নকল করেননি। নজরুল এমত অবস্থানে একজন উত্তর-আধুনিক নৈরাজ্যবাদী, প্রতিবাদমুখর অনলবর্ষী বিপ্লবী। সাইক্লোন সৃষ্টি ও সীমালঙ্ঘন তাঁর বৈশিষ্ট্য। ‘বিদ্রোহী’র ছন্দ, পুরো টেক্সট-এর কোনো কোনো অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে’র ‘আমি’-যুক্ত পুনরুক্তিচর্চার আংশিক সহগামী। ইংরেজি রেটোরিকে এই পুনরুক্তিচর্চাকে বলে anaphora। এর ফলে প্রতীতী আসে যে, ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ তিনি পড়েছিলেন, যদিও ‘বিদ্রোহী’র ছন্দ সুপরিকল্পিতভাবে চলে গেছে বিচিত্র পথে,এমনকি সর্বত্র। বিচ্ছিন্ন রবীন্দ্র সহগমনের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:
‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ থেকে:

“আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিব রে পরান ঢালি।
আমি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটি রচনা করেন তাঁর শৈশবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দেওয়ালের উপর দিয়ে সূর্যকিরণ উপভোগ করার অভিজ্ঞতা থেকে। ‘রবির কিরণ’ এখানে বহির্বিশ্বের প্রতীক। এই বহির্বিশ্ব প্রত্যাশী ও প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যপিপাসু কবির আত্মজৈবনিক উপাদানই এর প্রতিপাদ্য।
কাজী নজরুল ইসলাম এই ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ থেকে anaphora ‘আমি’, এবং সেই সঙ্গে মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির লালিত্য কর্জ করেন। ‘বিদ্রোহী’-তে মাত্রাবৃত্তের নমুনা নিম্নরূপ:
“আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই,
আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বির, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল;
আমি চল-চঞ্চল চকিতে ছমকি
ফিঙ দিয়ে দেই তিন দোল।
আমি চপলাচপল হিন্দোল।”
আরও উদাহরণ ‘বিদ্রোহী’র শেষ পর্যায় থেকে:
“আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর, অক্ষয়; আমি অব্যয় ।
আমি মানব-দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চিরদুর্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য।”
সুতরাং, সাদৃশ্য শুধু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের জায়গায়; এখানেই গুরুর কাছে শিষ্যের কর্জ। কবিতার ভাব-রাজ্য দুজনের দুই এলাকায়।
(দুই )
যোগ বা Yoga ও ধ্যান বা Meditation-এর সাথে কাজী নজরুল ইসলামের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাঁকে যোগাসনে বসে ধ্যানরত অবস্থায় দেখেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বক্তব্য আছে। যোগ বা Yoga-র কুম্ভ আসনে বসে পরিপক্ক যোগীর মতো ধ্যান বা Meditation করতেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিপ্লবী ও স্বদেশীরা ‘অনুশীলন’ ও ‘যুগান্তরে’ যোগ ব্যায়াম চর্চার আড়ালে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও মল্লযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতেন। নজরুল এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে ছাত্র থাকাকালে স্কুলের দুই শরীরচর্চা শিক্ষক, নিবারণ চন্দ্র ঘটক ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তাঁকে যোগ ব্যায়াম ও সন্ত্রাসবাদের অনুশীলন করাতেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ এসব কথা লিখেছেন। আমি ধারণা পোষণ করতে চাই যে,১৯২০-২১ সালে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে একই কক্ষে বসবাস কালেও নজরুল যোগ ব্যায়াম ও ধ্যান তথা meditation চর্চা করতেন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনার পরবর্তী পর্যায়ে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা অফিসটিকে নজরুল ওই যোগ ব্যায়াম এবং ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থল করে তুলেছিলেন। একজন দক্ষ যোগ-সাধক ও ধ্যানী হিসেবে নজরুলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর সমকালীন প্রায় প্রত্যেক বন্ধু।
মধ্যরাতের নিভৃতলোকে একজন ধ্যান মৌন কাজী নজরুল ইসলামের পক্ষেই সম্ভব ছিল ষড়-চক্রের অন্তর্দৃষ্টিতে নিজের আসনকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ মহিমান্বিত উচ্চতায় কল্পনা করা। Science of Meditation তাই বলে। শিবের বহুমাত্রিক শক্তিকেও নজরুল এই ধ্যান বা meditation-এর মধ্য দিয়েই একটি কাঠামোগত রূপে তাঁর চিত্তলোকে ধারণ করেন। কবি যে ধ্যান বা meditation থেকে সহসাই একটি দুর্দান্ত আবিষ্কার বা revelation পেয়েছিলেন, সে-সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন ‘বিদ্রোহী’ কবিতার শেষের দিকের একটি স্তবকে:
“আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!”
এভাবে, প্রায় অলৌকিকভাবে অর্জিত শক্তি ও প্রতিভাবলে সেদিন মধ্যরাতের পর তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব হয়:
“বল বীর–
বল, উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারই,
নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।”
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চ ন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর–
আমি চির-উন্নত শির।”
ধ্যানের মধ্য দিয়ে revelation পাওয়ার যোগ্যতালাভের টীকা বা স্মারক চিহ্ন হচ্ছে ললাটে একটি তৃতীয় নয়নের উপস্থিতি, যাকে কবি বলেছেন “দীপ্ত জয়শ্রী”। এটি কোনো সাধক যোগীর জন্যে উজ্জ্বল উদ্ধার অর্থেই একটি “দীপ্ত জয়শ্রী”।
কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার বই ‘নজরুলের শিল্পসিদ্ধি ও বিদ্রোহী’তে একই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে: “মূল চরিত্রটির প্রতীক শিব, আর তাকে কেন্দ্র করেই বলয়িত হয়েছে কবিতাটির সৃষ্টিবিশ্ব”। প্রকৃতই তাই। ‘বিদ্রোহী’ পাঠোদ্ধার করতে হলে ‘মহাভারত’ এর শিব ও তার বহুধা-রূপান্তর এবং দ্বন্দ্বমুখর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।
শিব, মহাকাব্য ‘মহাভারত’-এর চরিত্রটি, অজস্র রূপে- রূপান্তরে বর্ণিত হয়েছে এই কবিতাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। শিবের সেই পথ-পরিক্রমাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শ্লেষণ-বিপরীত শ্লেষণ-সংশ্লেষণ ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখে কবিতাটির একটি মোটাদাগের অর্থ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, তাঁর ‘Aesthetics of Nazrul’ গ্রন্থে, যেটির প্রকাশক Nazrul Institute, Dhaka । আমি মনে করি, কবিতাটির একটি স্তবকভিত্তিক paraphrasing দরকার। তারপর এর পাঠ- পর্যালোচনা ও তাত্পর্য উদ্ধার। সেই paraphrasing, পাঠ-পর্যালোচনা ও তাত্পর্য উদ্ধার বিষয়ক লেখাটি আমি উপস্থাপন করবো অতঃপর।
লেখক: কবি প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।



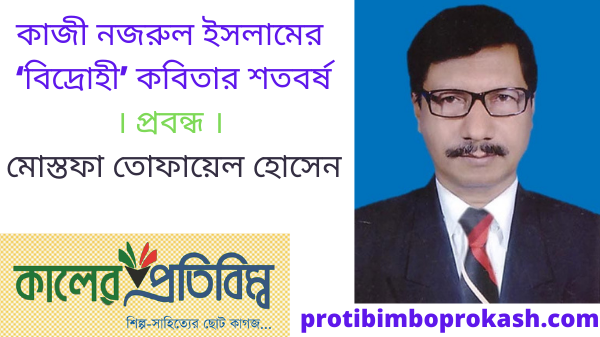


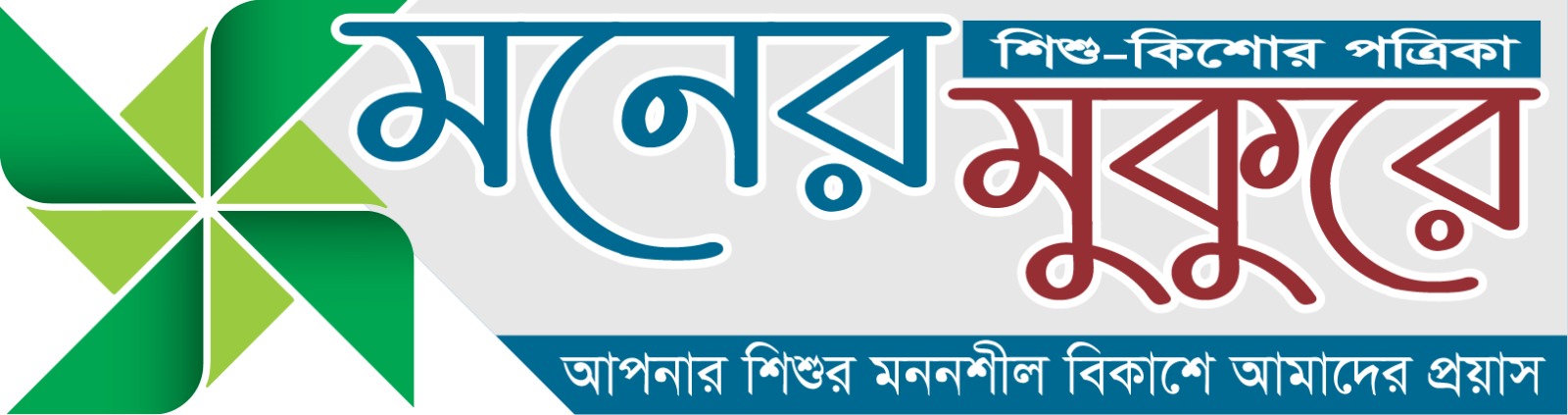
১ Comment
very good job; congratulations.