৩৩৬ বার পড়া হয়েছে
কবিতা ও বিভিন্ন বোধের উদ্ভাস
গোলাম কিবরিয়া পিনু
একটি কবিতা কীভাবে হয়ে উঠবে? তা কি পূর্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে? না, কবিও জানেন না–একটি কবিতা কীভাবে হয়ে ওঠে। এমন এক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে কবিতা নির্মিত হয়, যা কবিতা সৃষ্টির মুহূর্তে কবি হয়তো অনুভব করেন। আর কোন্ কবিতা কোন্ পাঠককে অনুরণিত করবে–তা অনেকটা কবিরও অজানা। সে কারণে এক অজানা পথের যাত্রীর মত কবিকেও হাঁটতে হয়–পথ খুঁজে নিয়ে যেতে হয়, কখনো-বা বহু বর্ণিল পথের দেখা পাওয়ার পর–একটি পথ নির্বাচন করে এগিয়ে যেতে হয়, তবে প্রকৃত কবি এগিয়ে যাওয়ার স্পর্ধায় সবসময়ে তৎপর থাকেন, মগ্ন হয়ে নিজেকে সংহত করেন।
কবিতা শুধু কি শব্দ? কবিতা শুধু কি ছন্দ? কবিতা শুধু কি অলংকার? কবিতা শুধু কি ভঙ্গি? কবিতা শুধু কি অর্থ? মনে হয় না। কবিতা অনেক কিছু মিলে এমন এক উদ্ভাস–যা ছোঁয়া না গেলেও, এক ধরনের লাবণ্য মনকে ছুঁয়ে নেয়, অভিনবত্বকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। কবিতা বহুতল ও স্তর তৈরি করে, পাঠককে নিয়ে যায় সেই স্তরে ও তলের গভীরে।
কবিতা কি শুধু কবির জন্য? না! কবি শুধু কি নিজের প্রেরণায় নিজের আত্মস্বপ্ন পূরণের জন্য লিখে থাকেন? না! কবি শুধু কি নিজের ব্যক্তিগত আশা ও আশাভঙ্গ নিয়ে দোলায়িত থাকবেন? না! কবিকে অনেক সময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে–অন্যের দুঃখ-কষ্ট, ভালো-মন্দও গ্রহণ করতে হয়। সমাজের এগিয়ে চলার গতি ও স্পন্দন অনুভব করতে হয়। বর্তমান সমাজ সরলরৈখিক অবস্থানে আগের মত নেই, সমাজ জটিল গ্রন্থি নিয়ে কবির কাছে আজ উন্মোচিত হয়। স্বভাব কবির সেই সরলতা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হয় তো আজকের কবি শিল্পের দাবী ও চাহিদা মিটাতে পারবেন না। এখন আরও লিপ্ততা, এখন আরও মগ্নতা কবির জন্য জরুরি হয়ে উঠেছে। একদিকে কবি তার নিজের বোধ ও দর্শনকে সংহত করেন, আবার অন্যদিকে সমাজের অন্যান্য মানুষের রুচি ও মনোভাব কবিতার প্রশ্রয়ে সূক্ষ্মভাবে নির্মাণ করেন। এ-এক মিথস্ক্রিয়া : গ্রহণ ও বর্জন, নেওয়া ও দেওয়া, অপূর্ণ ও পূর্ণতা।
কবি শুধু স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবেন? নাকি নৈতিক মান বজায় রেখে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে আন্তরিক ও সৎ থাকবেন? এসবও আজ আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। কবিরা ছোট সুবিধা ও নগদ-ধান্ধায় কবিতাকে ব্যবহার করবেন নাকি কবিতাকে এ-সবের ঊর্ধ্বে রেখে কবি নিজেকেও বাঁচাবেন, কবিতাকেও বাঁচাবেন–সেটা বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমাজে সুস্থতার কী মান হওয়া উচিত, তা উপলব্ধিতে নিয়ে এসে এক ধরনের টিকে থাকার সংগ্রাম কি কবির সংগ্রাম নয়? কবি তো যুগে যুগে এগিয়ে থাকা মানুষ। মানুষের এগিয়ে যাওয়ার জন্য দার্শনিকের ভূমিকায় অনেক ক্ষেত্রে কবিরা সূক্ষ্ণভাবে কাজ করেন। কবিরা বোধকে স্থূলতা থেকে–চোরাস্রোত থেকে বাঁচিয়ে গভীর ও সজীব অবস্থানে জীবন্ত রাখেন।
পাঠক হিসেবে লক্ষ করি–বর্তমানে কোনো কোনো কবি আধুনিকতার নামে ও পরিবর্তনের নামে কবিতাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিভ্রান্তিমূলক পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট। কোনো কোনো কবি পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে বিপর্যয়েরও সৃষ্টি করছেন, এর ফলে কবিতা হয়ে উঠছে কবিতার নামে খণ্ডিত এক পদ্ধতি মাত্র। শুধু বাঁক পরিবর্তনের ইচ্ছে নিয়ে চলার নাম এক ধরনের স্বাধীনতা হতে পারে কিন্তু আধুনিকতা মূর্ত নাও হতে পারে–কবিতায়। আধুনিকতা সমাজবিচ্ছিন্ন বিষয় নয় : সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়নির্দেশক দর্শন-চেতনা। শুধু পরিবর্তনের স্থূল চালচিত্র নিয়ে আধুনিকতা চিহ্নিত হতে পারে না। কবিতা সমকালীন হলেই–তা আধুনিক হবে, তা ঠিক নয়। শুধু কবিতার আঙ্গিক পরিবর্তন হলেই–আধুনিক কবিতা হয়ে ওঠে না–এরসাথে চেতনাগত বিষয়টিও যুক্ত। সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনের ফলে কবিতার পরিবর্তন হয়, তবে কবিরা–সমাজের অগ্রসর মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় বলেই তারা পরিবর্তিত চেতনাকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায় টেনে নিয়ে মানুষের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেন বা নতুনভাবে মানুষের ভাবনাজগতকে নির্মাণ করেন বা মানুষের বোধকে ভিন্ন দ্যূতিতে উজ্জ্বল করেন।
বাংলা কবিতা শুধু নয়, বিশ্বের অন্যান্য ভাষার কবিতাও ধারাবাহিকতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা প্রবহমানেরই নামান্তর। কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর পরিধি বেড়েছে, তবে তার মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক ও সাযুজ্য থেকেই যায়। মানুষের জীবনও চলছে চেতনার প্রবাহ নিয়ে, এই প্রবাহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিধিতে ব্যাপ্তি লাভ করলেও–অনেক ধারণা কাল পরিবর্তনের পরও একই থেকে যায়। কবিতার ক্ষেত্রেও এই ধরনের অপরিবর্তনীয় বিষয় ও শিল্পশর্ত লক্ষণীয়। যদি বলি–চর্যাপদ থেকে বাংলা কবিতার যে বিকাশ, সেই বিকাশের ধারায় সমকালীন বাংলা কবিতার অস্তিত্ব ও উজ্জ্বলতা। আর এই কারণে বাংলা কবিতার যে সম্ভাবনা তা অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বাংলা কবিতার যে বৈশিষ্ট্য ও ব্যঞ্জনা রয়েছে, সেই প্রবহমান শক্তিকে ধারণ করেই সমকালীন বাংলা কবিতার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করতে হবে।
বিভিন্ন ধরনের কবিতার অস্তিত্ব থেকে যায়। আর এই বিভিন্ন ধরনের কবিতা শুধু সাম্প্রতিকালেই লেখা হচ্ছে না, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নকালে তা লেখা হয়েছে। এ কারণে কবিতাকে একক সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তাই বলে–কবিতাকে পিঠমোড়া করে নিয়ে নৈরাজ্যের হাটে বেচাকেনা করাও সমীচীন নয়। কবিতা বহুবিধ সংজ্ঞার মধ্যে থেকেও ধারাবাহিকতায় এক ধরনের অন্তঃপ্রাণ নিয়ে বাঁচে, বেঁচে থাকবে। কবিতা বহুবিধ শৈলীর সমন্বয়ে অভিজ্ঞতা-অনুভূতি-আবেগ নিয়ে প্রাণ পায়। আর সেজন্য কবি মাত্রই জানেন–ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা আর বহুবিধ অলংকারের তাৎপর্য। তবে যান্ত্রিকতার বাইরে কবি মস্তিষ্কের বহুবর্ণিল অনুরণন প্রকৃত কবিতায় রূপ পেতে দেখি। যে কবিতা পাঠককে কাব্যরসে সিক্ত করে এক ভিন্ন শিল্পবোধে চঞ্চল করে তোলে, দোরখোলা মুক্ত দিগন্তে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত শুধু করে না, দর্শানুভূতিতে বিভিন্নমুখী তাৎপর্য সৃষ্টি করে, তখন তা প্রকৃত কবিতার উদাহরণ হয়ে ওঠে।
আশার কথা–সমকালীন কবিতায় ছন্দ শুধু গুরুত্ব পাচ্ছে না, মিলবিন্যাসের চমকপ্রদ ব্যবহারও আমরা লক্ষ করছি। ছন্দ ও মিলের যে এক ধরনের শক্তি রয়েছে–তা এখন শুধু প্রতীয়মান হচ্ছে না, পূর্বেও প্রতীয়মান হয়েছিল। বাংলা কবিতার (শুধু বাংলা কবিতা কেন, অন্য ভাষার কবিতায়ও লক্ষ্যণীয়) ধারাবাহিকতায় ছন্দের একটি শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। তাই বলবো–ছন্দের প্রত্যাবর্তন কবিতায় আসুক, আরও নিরীক্ষায় সংহত হোক। সত্তর-আশি বা পূর্বের কবিতায় ছন্দ যে একেবারে ছিল না, তা কিন্তু নয়। কবিতায় ছন্দ ব্যবহারে উদাসীনতা আমরা লক্ষ করেছি চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের কবিদের ক্ষেত্রে। সেই সময় থেকে বাংলা কবিতার বিভিন্ন পর্যায়ে ছন্দকে অগ্রাহ্য করে কবিতার অনেক মূল্যমানকেই নষ্ট করার মানসিকতাও লক্ষ করা গেছে। পত্র-পত্রিকার প্রাচুর্য ও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ছোট পত্রিকার আওতায় কাব্যচর্চার উন্নাসিক প্রবণতার ফলে কবিতা শুধু ছন্দের বিপরীতে দাঁড়ায়নি, বিভিন্ন অলংকারের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছে, এরফলে কবিতা শিথিল ও অনায়াস লেখনীর কসরৎ হয়ে দাঁড়ায়–এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। তবে বলবো না–ছন্দ ছাড়া কবিতা হয়নি বা হবে না কিংবা ছন্দেও ভাঙা-গড়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে না।
বিভিন্ন কবির কবিতায় বিভিন্ন বিষয় ও শৈলীর উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। কবিতা স্পষ্ট-অস্পষ্ট, উচ্চকণ্ঠ-নিম্নকণ্ঠ, আখ্যানধর্মী-নাট্যধর্মী-লিরিকধর্মী ইত্যাদি রকমের হতেই পারে। পাঠকের সাথে কবির এক ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্য থেকেই যায়–এই উদ্দেশ্য যে কোনো শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে, সমকালীন কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্য হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যে কবিতা এককালে দুর্বোধ্য, তা পরবর্তিকালে বোধগম্য হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে–রুচি, পাঠস্পৃহা ও অন্যান্য কারণে। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু কবিতা লেখা হচ্ছে কবির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ও কবিতার সহজ প্রকাশ-সুযোগের জন্য; এমন কবিতা পাঠকের সাথে কাঙ্ক্ষিত সংযোগ স্থাপন করতে পারছে না। এসব কবিতায় না আছে ভাবের সঙ্গতি, না আছে ছন্দের সঙ্গতি, না আছে অলংকারের সঙ্গতি, না আছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গতি। এসব তথাকথিত কবিতার ফলে কবিতার পাঠক কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু পড়ছে না, কবিতা হয়ে উঠেছে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে সবচেয়ে সহজলভ্য বস্তু। নিছক দুরুহতা ও অস্পষ্টতা নিয়ে কবিতাকে নৈরাজ্যের ভেতর ঠেলে দিয়ে কবিতার সম্ভাবনা ও মূল্যকে নষ্ট করা সমীচীন নয়। কবিতাকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপকল্পে বিভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে কবিতাকে উজ্জ্বল করার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে কেউ কেউ বর্তমানে সৃজনমুখর, এমন কবিদের হাতেই সমকালীন কবিতার সম্ভাবনা বেশি।
কবিতা সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো শিল্পমাধ্যম নয়। তবে কবিকে সামাজিক দায় নিয়ে কবিতা লিখতে হলেও–তার সেই দায় পালনের সীমা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হলে–কবিতার সৌন্দর্য নষ্ট হবে না–সেটা বুঝতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় একটি কবিতা শিল্পশর্ত পূরণ করেই সামাজিক দায় বহনের শক্তি অর্জন করতে পারে। বাংলা কবিতার ধারায় কখনো কবিতা ধারণ করেছে বৌদ্ধ সাধনার বিষয়–যেমন চর্যাপদের দোহা, কখনো কৃষ্ণকথার শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৈষ্ণম পদাবলী, রামায়ণ-মহাভারত কিংবা বিংশ শতাব্দীর সময়ে মানুষের জীবন, সংগ্রাম, পরাধীনতা, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, নগরজীবনসহ সমাজের নানা পরিধির দিগন্ত। সমাজজীবন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরের নব-নব সম্ভাবনাকে কবিতা ধারণ করে থাকে। কবির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে–কী দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বর্তমানের সমাজ ও সামাজিক জীবনকে দেখবেন, সমাজের কোন্ পরতে তার কাব্য-আলো ফেলবেন, কোন্ জিনিসটি বর্জন করবেন বা বিকশিত করবেন। কবিতা মানুষের জন্যই–ভালো কবিতার শিল্প-সৌন্দর্য স্বতঃস্ফুর্ত ও আনন্দময় অনুভূতির জন্ম দিয়ে থাকে।






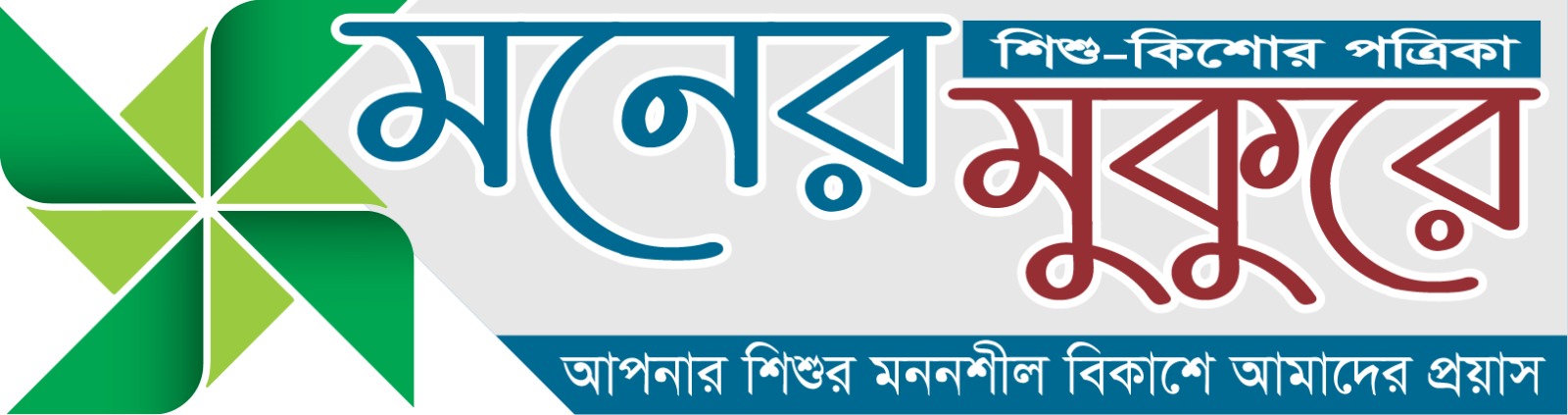
১ Comment
কবির আভ্যন্তরীণ বোধকে খুব দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রিয় লেখক । পাঠে মুগ্ধ হলাম । ❤️?