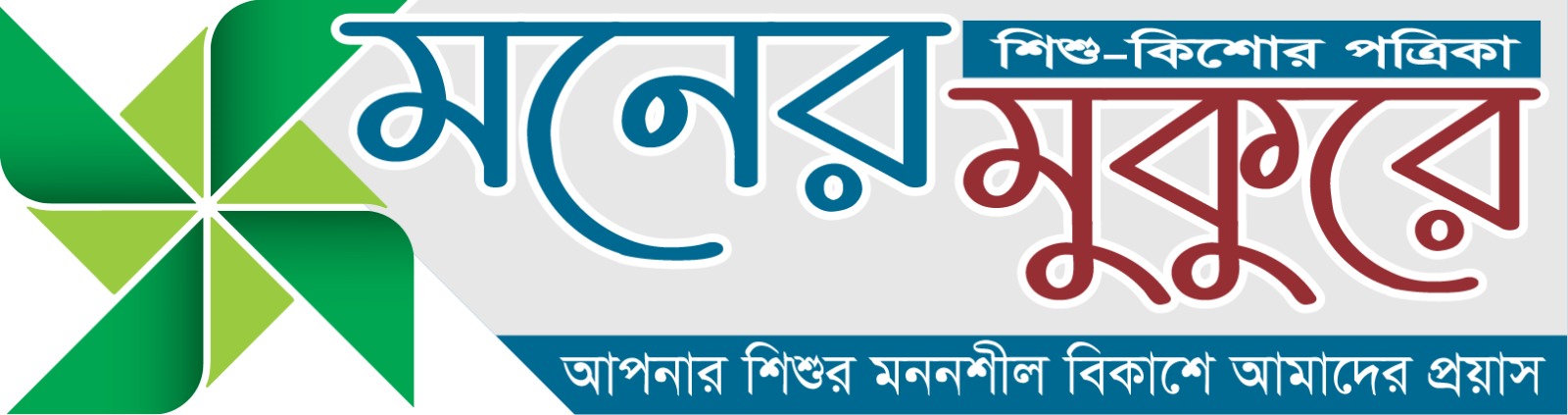৩৯৯ বার পড়া হয়েছে
প্রকাশিতব্য উপন্যাস ‘ কানফুল ‘। পান্ডুলিপি পড়ে আলোচনা করেছেন খ্যাতিমান কবি ও কথাসাহিত্যিক ড. শাহেদ ইকবাল। আগ্রহী হলে আপনিও তাঁর আলোচনা/মতামত পড়ে দেখতে পারেন। পড়তে সময় লাগবে মাত্র ৩মিঃ৩৭ সেকেন্ড!
“বাস থেকে নেমে জিন্নত আলী রাস্তা পার হয়। কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা হবে। ওখান থেকে বাসা পর্যন্ত সে রাস্তাটুকু হেঁটে যেতে চায়। রাজ্যের চিন্তা তার মাথায়। নিচের দিকে তাকিয়ে সে হাঁটছে। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ হয় একটা ডাকে।
ও ভাই, ভাইজান, ও ভাইজান, একটু হুনেন। ও ভাই একটু হুনেন না। আরে, ও ভাই।
জিন্নত আলী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মেয়ে কণ্ঠের ডাক। গলির ভেতর থেকে ডাকটা আসছে। তাকে ডাকছে। জিন্নত আলী আরো দ্রুতবেগে পা চালায়। ফিরে দেখার অর্থ নির্ঘাত কোনো বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছে।”
কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের ‘কানফুল’ উপন্যাসের শুরুটা এরকম। পাঠকের মনে হবে উপন্যাসের নায়ক কোনো নিশিকন্যার ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে। হয়তো এটা কোনো বিশেষ পাড়ার গল্প। কিন্তু কাহিনী যতই সম্মুখে গড়াতে থাকবে, ততই দৃশ্যপট বদলে যেতে থাকবে। পাঠক মুখোমুখি হবেন একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত নগরচারী পরিবারের নাটকীয় টানাপোড়েন ও শ্বাসরুদ্ধকর গতিময়তার সাথে। উপন্যাসের নায়ক যেন রাজপথ থেকে নয়, জীবন থেকেই পলায়নের চেষ্টা করছেন। সেই কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে আছে শিহরণ জাগানো উত্তেজনা ও বাঁকবদল।
উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জীবিকার অন্বেষণে নগরমুখী এক মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেই পরিবারের কেন্দ্রে আছে জিন্নত আলী ও সাহিদা। তাদের তিন সন্তান। অপু, নবু ও চায়না। জিন্নত আলী জীবিকার অন্বেষণে এই পরিবারকে নিয়ে রাজধানীতে আসে। একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মে সুপারভাইজারের চাকরি নেয়। এক পর্যায়ে সেই চাকরি চলে যায়। শুরু হয় ভাগ্য বিপর্যয়। নানা ঘটনায় স্বপ্নপূরণ নামক আরেকটি কোম্পানীতে চাকরি পায়; কিন্তু বেতনভাতা হয়ে পড়ে অনিয়মিত। দুই ছেলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বকেয়া বাড়িভাড়া জমতে থাকে। দেনার দায়ে একটার পর একটা বাড়ি ছাড়তে হয়। সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বন্ধক রাখতে হয়। শখের পালংক থেকে শুরু করে টিভি পর্যন্ত চলে যায় বাড়িওয়ালার হাতে। বাকি থাকে একজোড়া কানফুল। যৌবনের স্বর্ণালী সময়ে স্ত্রীকে উপহার দেওয়া কানফুল। শেষপর্যন্ত কি এই কানফুলও হাতছাড়া হবে?
উপন্যাস এই পর্যায়ে চরম নাটকীয়তা লাভ করে। একটি আটপৌরে নাগরিক উপন্যাস সহসা রূপান্তরিত হয় বহুমাত্রিক বিশ্বজনীনতায়। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনসংগ্রাম রূপান্তরিত হয় শাশ্বত মূল্যবোধের উপাখ্যানে। এই মূল্যবোধের নাম মাতৃত্ব। চিরায়ত গ্রামবাংলায় নোলক যেমন মাতৃত্বের প্রতীক, তেমনি কানফুলও মাতৃত্বের প্রতীক। সেই প্রতীকের কাছে হার মানতে হয় দুই বখাটে পুত্র সন্তানকেও। যে মায়ের বকুনিতে মনের দুঃখে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, সেই মায়ের কানফুল বন্ধক দিতে হচ্ছে শুনে দুই ছেলের হৃদয়ে অন্যরকম আবেগের প্লাবন খেলা করে। চেনাজানা নাগরিক জীবনের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে দুই পুত্রের স্মৃতিতে ভাসতে থাকে স্বর্ণালী শৈশব, যে শৈশবে কানফুল দুলিয়ে দুলিয়ে এই মা (সাহিদা) তাদের ঘুম পাড়াতো। অপু ও নবু কিছুতেই এই শাশ্বত মাতৃরূপের ছবি থেকে আর বেরুতে পারে না। চিরকালের বখাটে চরিত্র পায়ের তলায় পিষে মেরে তারা মায়ের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। যে কোনো মূল্যে মায়ের কানফুল ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিভাবে ফেরত নেবে? তারাও তো কপর্দকহীন। উপন্যাসের পাতায় সময় যেন থমকে দাঁড়ায়। বড় ছেলে অপু নিজের কিডনি বিক্রি করে দেয়। কিডনি বিক্রির টাকা দিয়ে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে মায়ের কানফুল ফেরত নেয়। যে গ্রামে কখনও ফিরবে না বলে পণ করেছিল বাবা-মার হাত ধরে সেই গ্রামের পথে যেতে যেতে বলে, ‘যারা সামান্য ভাড়ার টাকার জন্য ভাড়াটিয়াকে অপমান করে, জিনিসপত্র রেখে দেয়, কয়েক মাসের ভাড়ার জন্য মায়ের কানফুল রেখে দেয়, আত্মসাৎ করে, তারাই ছোটলোক।…এমন পিশাচ-রাক্ষসের শহরে আমরা আর থাকব না।’
বিবর্তনের বর্ণিল পথে মানব সভ্যতা যতই বিকশিত হয়েছে, ততই তার কাছে দৃশ্যমান জীবন ও জগৎ প্রাধান্য পেয়েছে। জৈবিক তৃপ্তির উপযোগ, ভৌত অবকাঠামো, পুঁজি ও উৎপাদনের মালিকানা তার কাছে শ্রেষ্টত্বের মাপকাঠি হয়েছে। দর্শনের উপজীব্যও হয়েছে দৃশ্যমান ভৌতজগত। ত্যাগের দর্শন উপেক্ষিত হয়েছে; প্রাধান্য পেয়েছে ভোগের দর্শন। তারপর একসময় কারও কারও মোহভঙ্গ হয়েছে। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ উপলব্ধি করেছেন, এটা সভ্যতার বিকাশ নয়, এটা সভ্যতার অধঃপতন। মানবাত্মার বিকাশ (Spiritual Development) ছাড়া সভ্যতার কোনো বিকাশ হতে পারে না। যুগসন্ধিক্ষণের এ মিছিলেরই পুরোধা ছিলেন লিও টলস্টয়, ভিক্টর হুগো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। জাগতিক পংকিলতার মাঝেও তাঁরা মানবাত্মার অনুসন্ধান করেছেন; জীবনের পরম সত্যকে জেনেছেন গভীর মমতায়।
বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় চলছে এক গ্রহণের কাল। একদিকে চরম নৈরাজ্য ও অস্থিরতা, আরেকদিকে নিয়ন্ত্রণহীন ভোগের পাপ-রাজত্ব। এ দুয়ের সম্মিলনে বিশ্ব মানবতা দিকভ্রান্ত, সংশয়গ্রস্ত ও যন্ত্রণাকাতর। দু’টি বিশ্ব সমর তাকে দিয়েছে কেবল ধ্বংস আর হতাশা। এ হতাশা যখন ব্যক্তিজীবনকেও গ্রাস করে, যখন দুয়ারগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায়, যখন পৃথিবীর সব আলো নিভে যায়, সব সুর থেমে যায়, দু’চোখের জানালায় খেলা করে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, তখন ডুবন্ত মানুষ চিরায়ত সম্পর্কগুলো আঁকড়ে ধরতে চায়। এ বিশ্বজগতে মা তো তেমনই এক চিরায়ত সম্পর্ক, যার কোন জাতি-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায় নেই; কোন শিরোনাম নেই। যে পরিচয়েই তাকে বন্দি করা হোক, শেষমেষ সে হয়ে থাকবে বিশ্বজনীন। আকাশ ও সূর্যের যেমন কোন জাতিভেদ থাকে না।
কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের গদ্যরচনার একটি নিজস্ব শৈলী আছে, যা বর্তমান উপন্যাসের মধ্যেও দৃশ্যমান। মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়ে উদারহস্তে লোকজ উপকরণ সরবরাহ করেছেন। পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের দোদুল্যমানতাকে একের পর এক দৃশ্যপটে হাজির করেছেন। ঘটনার ঘনঘটায় স্বপ্ন, অশ্রু, হিংসা, ঘৃণা, মোহ, প্রতীক্ষা ও বিসর্জনকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। জীবনযুদ্ধের গ্লানি ও কদর্যতাকে দারুণভাবে চিত্রায়িত করেও বাঙালি সংস্কৃতির শিকড়কে হারিয়ে যেতে দেননি। এখানেই একজন কথাসাহিত্যিকের পূর্ণতা ও সফলতা।